বাংলাদেশের ইংরেজি সাহিত্যিক
বাংলাদেশের বহু লেখকই এখন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করছেন। তাঁদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নজর কেড়েছেন। বাংলাদেশের ইংরেজি ভাষার সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আয়োজন
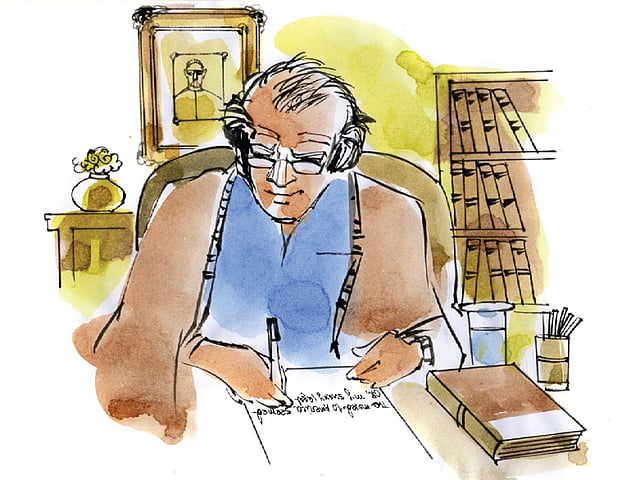
বাংলাদেশের লেখক যেখানে বাংলায় লিখে পাঠক পান না, পেলেও ৩০০ বই বিক্রি করতে এক বইমেলা থেকে আরেক বইমেলা পর্যন্ত লেগে যায়। সেখানে তিনি ইংরেজিতে কেন লিখবেন, এ রকম প্রশ্ন বছর দশেক আগেও উঠতে শুনেছি। এখনো ওঠে, তবে তেমন জোরেশোরে নয়, যেহেতু ইংরেজি উপন্যাস অথবা কবিতার বইও ৩০০ বিক্রি হয়ে যায় কারও কারও, এক বইমেলাতেই। বাংলা বইয়ের বিক্রি তো অনেক বেশি। পাঠক বাড়ছে, প্রকাশক এগিয়ে এসেছেন, বই বিক্রির নানা পথও খুলছে। তবে এই প্রশ্নের একটা উত্তর রাখা আছে মানুষের সৃজনশীলতা আর লেখালেখির ইতিহাসে। ওই ইতিহাসে ভাষা নয়, লেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে একজন বাংলায় লেখেন, সে কারণে আরেকজন ইংরেজিতে লেখেন। তাঁদের কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার কথা নয় কারও কাছে, বড়জোর বলতে পারেন, না লিখে পারি না, তাই লিখি।
এ উত্তরটা শামসুর রাহমান দিতেন, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, কেন লেখেন?
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে লিখেছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন। এর আগে রামমোহন রায় লিখেছেন। সময়টা ছিল বাঙালির জ্ঞানলোক পাওয়া এবং ছড়ানোর কাল। ইংরেজি ছিল রাজভাষা, ‘এলিট’ ভাষা, এ ভাষা ছিল পশ্চিম থেকে জ্ঞান নিয়ে আসার প্রধান বাহন। ইংরেজি এখন আর রাজভাষা নয়, এককালের প্রজারাও ইংরেজি দখল করে, নানা কাজে ব্যবহার করতে করতে সেটি নিজের মতো করে নিয়েছেন। এখন একক বিশিষ্ট এবং কেন্দ্রীয় ইংরেজি বলে কিছু নেই, আছে নানা ইংরেজি। এই প্রতিটি ইংরেজিতে মিশেল ঘটেছে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের সংস্কৃতি, লোকাচার এবং জীবনযাত্রার নানা উপকরণ। নানা ইংরেজির ডালায় বাংলাদেশের ইংরেজিও আছে। মধুসূদনকে ইংরেজ পাঠক যে অবজ্ঞা দেখিয়েছে, কায়সার হককে এখন তা দেখাবে না। কারণ, মধুসূদনের কালের ইংরেজ বিশ্বায়নের এই যুগে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পাল্টে গেছে। তার আভিজাত্যবোধ অনেকটা কেড়ে নিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, জাপানি, আরবি ও তুর্কি সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ, ভারতীয় বা আফ্রিকার লেখকদের মূল ইংরেজি উপন্যাস, গল্প অথবা কবিতা। এখন কায়সার হকের কবিতা জায়গা করে নিয়েছে কেন্দ্রে, কেন্দ্র যেহেতু এখন একক নিয়ন্ত্রণকারী কোনো কর্তৃপক্ষ নয়; সে আজ দুর্বল, কেন্দ্র তার কেিন্দ্রকতা হারিয়ে হাত পাতছে এককালের প্রান্তের কাছে।
মধুসূদন মর্মবেদনা নিয়ে মাতৃভাষার কাছে ফিরেছিলেন। মাতৃভাষাটা যে প্রধান, দ্বিতীয় যেকোনো ভাষা থেকে সেটি তিনি বুঝেছিলেন। এখন যাঁরা ইংরেজিতে লিখছেন বাংলাদেশে, তাঁরাও বিষয়টি জানেন। কিন্তু তরুণ অনেক লেখকের কাছে, বিশেষ করে যাঁরা বিদেশে বড় হয়েছেন, বাংলা শুধু কাগজে-কলমে মাতৃভাষা। আরও অনেকের মাতৃভাষাটা নড়বড়ে, ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার জন্য। কিন্তু তাঁদের ইংরেজি লেখায় বড় একটা অংশজুড়ে থাকে বাংলাদেশ। এ জন্য অনেক ইংরেজির এই যুগে কেন কেউ ইংরেজিতে লিখছেন, এ প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা লিখছেন, তাঁদের অনেকে বলবেন, স্বাচ্ছন্দ্যে এই ভাষায় লিখতে পারি, তাই। আর বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ আর আমাদের প্রজন্মের চিন্তাভাবনাগুলো বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি, তাই।
বাংলাদেশের ইংরেজি লেখকের দায়বদ্ধতা এখন দেশের কাছে, ইতিহাসের কাছে। এ জন্য তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও ইংরেজিতে লিখেছেন। ১৯০৫ সালে তাঁর সুলতানাস ড্রিম বেরিয়েছিল। তিনি কোনো আভিজাত্য চিন্তা থেকে লেখেননি। জাতে ওঠার তাগিদ থেকেও লেখেননি। লিখেছিলেন একটি প্রতিবাদী অবস্থান থেকে। নারীকে তিনি দেখেছিলেন দুই মাত্রার নিম্নবর্গীয় হিসেবে। তাঁরা উপনিবেশের শাসনে নিষ্পেষিত, পুরুষের মতোই—সেটি ছিল তাঁদের প্রথম নিম্নবর্গীয়তা; দ্বিতীয়টি ছিল ওই উপনিবেশ-শাসিত নিম্নবর্গীয় পুরুষের অধীনতা। সুলতানাস ড্রিম-এ তিনি পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে, পুরুষকে মর্দানার চার দেয়ালে ঢুকিয়ে, নারীদের শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে এক অসাধারণ নারীবাদী গল্প লিখলেন, যা পুরুষতন্ত্রের দুর্বলতাগুলোকেই শুধু দেখিয়ে দিল না, নারীর শক্তির জায়গাগুলোকেও চিহ্নিত করল। উপনিবেশবাদবিরোধী লেখা হিসেবে সুলতানাস ড্রিম নিয়ে আপ্লুত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না ইংরেজদের। নারীবাদী তত্ত্বের বিরল একটি আখ্যান হিসেবে এই লেখা নিয়ে উদ্বেলিত হওয়ার কথা ছিল না ইংরেজ পুরুষতন্ত্রেরও। ইংরেজিতে লেখা এই রচনাটি অবহেলিতই রয়ে গেল দীর্ঘদিন। এক শ বছর পর, লেখাটি স্থান পেতে শুরু করল পশ্চিমের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। অনেক তুখোড় নারীবাদীকে পেছনে ফেলে এখন পশ্চিমের একাডেমিয়ায় রোকেয়ার অবস্থান ক্রমাগত সামনে যাচ্ছে।
বাংলাদেশের ইংরেজি লেখক কেন ওই ভাষায় লেখেন? প্রশ্নের উত্তরে তাই বলা যায়, তিনি লেখেন, যেহেতু এই ভাষাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। লেখেন যেহেতু এককালের প্রান্ত এখন স্বাধীন একটি দেশ—কেন্দ্র এবং এখানে লেখার অনেক বিষয় তৈরি হয়ে গেছে।
উপনিবেশী প্রভুদের এবং কেন্দ্রের কর্তৃত্ববাদী সাহিত্যকে লিখে জবাব দেওয়া, উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্যতত্ত্বে যাকে বলা হয় ‘রাইটিং ব্যাক’, এখন যাঁরা লিখছেন, তাঁরা এ সময় লিখে জবাব দিচ্ছেন বিশ্বায়নের ঠাকুরদের কর্তৃত্ববাদী সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যারা নির্ধারণ করে কাদের বই ছাপা হবে থেকে কারা বড় বড় পুরস্কার পাবে, সেসব বিষয়।
ইংরেজিতে এক দত্ত কবিতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখা এত ব্যাপক যে কয়েক খণ্ডে ম্যাকমিলান সেগুলো প্রকাশ করেছে। নীরদ চৌধুরী ইংরেজিতে তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন, আরও অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁদের লেখালেখির উদ্দেশ্যটাও আমাদের হিসাবে নিতে হবে, যদি বাংলাদেশি ইংরেজি লেখকের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। এক দত্ত লিখেছেন রোমান্টিক মেজাজে, একজন রোমান্টিকের মতো তিনিও ভেবেছেন, ভাষায় কী আসে-যায়, মেজাজটাই তো প্রধান। এই ভাষায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁর সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত জীবনে এটিই ছিল শৈল্পিক প্রকাশের প্রধান ভাষা।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিশ্বকে মাথায় রেখে। তিনিই আমাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বিক লেখক। তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, বাংলাকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ইংরেজিকে তিনি দ্বিতীয় একটি ভাষা হিসেবে নিয়েছেন এবং সেটি যেহেতু তৎকালীন কেন্দ্রের ভাষা, সেই ভাষায় পৌঁছাতে চেয়েছেন কেন্দ্রের কাছে, তাঁর ভারতীয় ও বাঙালি ভাবনা–দর্শন ও চিন্তা নিয়ে।
নীরদ চৌধুরী ভারতে কলকে না পেয়ে ভেবেছেন পশ্চিম তাঁকে সেই কলকে দেবে। কিন্তু হায়, পশ্চিমের মন এত সহজে গলে না। নীরদ চৌধুরী ইংরেজি লেখালেখিতে একটা ফুটনোট হিসেবেই থেকে গেলেন। অর্থাৎ এই তিনজনের লেখালেখির হিসাব করলে দেখা যাবে, রোমান্টিকতার একটা প্রভাব ছিল শুরুতে, যার কারণে লেখাটাকে গুরুত্ব দেওয়া হলো, ভাষাটাকে নয়। এরপর ছিল একটি শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিশ্বকে কিছু চ্যালেঞ্জ জানানোর বিষয়। এতে ভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেল ভাষাস্রষ্টার আত্মবিশ্বাস এবং তাঁর বিষয়বস্তু। এর পাশাপাশি পশ্চিমের চোখে পড়ার একটা বাসনাও ছিল, যেন পশ্চিমের, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সাহিত্য বিচারে উতরে গেলে বড় একটা কিছু পাওয়া হয়ে যাবে। এক লাফে আমাদের সময়ে এসে পৌঁছালে, আশ্চর্য, এই সবগুলো চিন্তার ও চিহ্নের প্রতিফলন আমরা দেখব। আমাদের ইংরেজি লেখকেরাও লিখছেন নানা কারণে। শুরুতে ‘এলিট’ এই ভাষায় লিখে ইংরেজ এস্টাবলিশমেন্টে একটা জায়গা পাওয়ার ইচ্ছা যেমন ছিল, নিজের মতো করে লিখে কিছু প্রতিবাদ, কিছু বিপরীত কথা এককালের কেন্দ্রে, ‘এলিট’ সাম্রাজ্যে পাঠানোর ভাবনাটাও ছিল। আমিও আপনাদের মতো লিখতে পারি—এ রকম আত্মপ্রসাদ ছিল। আর এ রকম ভাবনায় ছিল একটা ছেলেমানুষি তৃপ্তিও। কিন্তু দিন যত গেছে, এ রকম চিন্তা থেকে লেখকেরা বেরিয়ে এসেছেন।
এখন অন্তত আমার চোখে, ‘এলিট’ উঠোনে চেয়ার পেতে বসার মানসিকতাটা প্রধান নয়। এখন বরং এ রকম ভাবনা কাজ করে যে ইংরেজি আমারও একটি ভাষা, দ্বিতীয় অথবা সে রকম; এবং এটিতে আমারও একটি অধিকার আছে, যেহেতু এতে আমার স্থানিকতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটানো যায়। এখন যাঁরা লেখেন, তাঁরা ইতিহাস, সময় ও মানুষ নিয়ে অনেক বেশি মনোযোগী। এ সময়ের লেখক কোনো হীনম্মন্যতায় ভোগেন না, যেহেতু তিনি বাংলাদেশি হলেও বিশ্ব নাগরিক। তিনি বরং ব্যস্ত তাঁর গৌরবের জায়গাগুলো চিহ্নিত করে বিশ্বকে সেসব দেখানোয়।
একসময় ইংরেজিতে লেখালেখিটা ছিল শৌখিন একটা কাজ। একটা কৈফিয়ত যেন থাকত সেই লেখার পেছনে (আমি ভাষাটি জানি, সে জন্য সেটি ব্যবহার করছি)। এখন ইংরেজিতে লেখাটা স্বাভাবিক সাহিত্যকৃত্যের একটি অংশ। এর আলাদা কোনো মহিমা নেই।
২.
১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশ ছিল প্রান্তের দেশ। ঢাকা ছিল মফস্বল, একটি প্রদেশের রাজধানী হলেও।
কিন্তু কী এক রসায়নে এর শিল্প-সাহিত্যে শুরু হলো জোয়ার। এক দশকেই—পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতার বড় বড় সব ঢেউ আমাদের চিত্রকলা, গল্প, উপন্যাসে—শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সৈকতে আছড়ে পড়ল, যেন নতুন শক্তি নিয়ে জাগল।
ষাটের দশকে এসে বুঝলাম, আমরা বিশ্বের সঙ্গে আছি, গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকার মানুষ নই আমরা, আমরা একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের জাতি। আমাদের সাহিত্য এক লাফে এক শ বছর পার হয়ে গেল। আমাদের সময় এল এই বিরল অর্জনকে আরও উচ্চতায় তুলে ধরার। এবং যখন বাংলায় আমরা একটির পর একটি বড় কাজ করে যাচ্ছি, কেউ কেউ ভাবলেন ইংরেজিতেও কেন লিখব না। আমার বিচেনায় এটি ছিল আমাদের আধুনিকতা, বিশ্বদৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় আমরা পাস করেছি। তার পরও শুরুতে যখন রাজিয়া খান আমিন বা নাজমুদ্দিন হাশেমের মতো লেখকেরা লিখেছেন, তাঁরা ভেবে নিয়েছেন, কম পাঠকই পড়বেন তাঁদের বই এবং ওই পাঠকেরা হবেন অনেকটাই সমমনা।
এ জন্য ইংরেজি গল্প-উপন্যাস ছাপা হতো কালেভদ্রে। তুলনায় কবিতার সংখ্যা ছিল একটু বেশি। প্রবন্ধ লেখা হতো প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার প্রয়োজনে। দু-এক ইংরেজি কাগজের সাহিত্য পাতা অথবা খান সারওয়ার মুর্শিদের নিউ ভ্যালুজ-এর মতো উঁচু মানের জার্নাল ছিল এই লেখালেখির বাহন।
ইংরেজি লেখালেখিতে গতি এল স্বাধীনতার পর। সংগত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ শুধু জাতি হিসেবে আমাদের পুনঃঅধিষ্ঠান ঘটাল, তা-ই নয়, আমাদের সাহিত্যে—বাংলা, ইংরেজি, চাকমা—সব ভাষাতেই একটা চিরস্থায়ী আসনও পেতে নিল। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দিল আকাশটা ছোঁয়ার স্বপ্ন ও সাহস।
সত্তর-আশির দশকজুড়ে ইংরেজি লেখালেখি চলেছে ঢিমেতালে, নিজের মতো করে। স্বাধীনতার পর পর উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে হটিয়ে দেওয়া হলে শিক্ষার বিস্তার যেমন বাড়ল, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তাটাও প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু দুর্বল হলো ইংরেজি চর্চা। অবশ্য দ্রুতই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকলে ইংরেজি লেখালেখির কিছু পাঠক পাওয়া গেল। তবে ইংরেজি মাধ্যমের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্য ইংরেজি লেখালেখির সঙ্গেই যেন লেগে গেল ‘এলিট’ চিহ্নটি।
সে অবস্থা থেকে বেরোতে কিছু সময় লাগল। সত্তর-আশির দশকেই দেখা গেল, ইংরেজি লেখালেখির বিষয়বস্তু নেওয়া হচ্ছে আমাদের জীবন থেকেই। এরপর যখন নব্বইয়ের দশক থেকে লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বাড়ল, ওই বিষয়বস্তুই এসব লেখালেখির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিল। এখন কেউ বলবে না, ইংরেজি লেখালেখি এলিটদের কাজ। কায়সার হকের পাবলিশড ইন দ্য স্ট্রিটস অব ঢাকা শামসুর রাহমান অথবা শহীদ কাদরীর কবিতার মতোই বাংলাদেশের, ঢাকার জীবনকেই তো উপজীব্য করে লেখা। আমাদের শক্তির, আমাদের গর্বের জায়গাগুলোকেই তো তুলে ধরে এই কবিতাগুলো।
ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকেরা এখন বাংলাদেশের ইংরেজি সাহিত্য পড়েন নিজেদের অথবা নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতিকে বাংলাদেশি লেখকদের চোখ দিয়ে দেখার জন্য নয়—ওই প্রাচ্যবাদী চিন্তার দিন বহু আগে শেষ হয়েছে—বরং তাঁরা পড়েন বাংলাদেশকে জানার জন্য, তা মনিকা আলি বা মঞ্জু ইসলামের বর্ণনায় ইংল্যান্ডের বাঙালি ডায়াসপরাকে জানতে অথবা তাহমিমা আনামের ভাষ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে। এখন অনেক তরুণ ইংরেজিতে লিখছেন, যাঁদের সবার নাম নিতে গেলে অনেকটা জায়গা লাগবে—কাজী আনিস আহমেদ, সাজিয়া ওমর, ফারাহ গজনবি, মাহমুদ রহমান, মারিয়া চৌধুরী, মুনিজ মজনুর, সাদ হোসেন, শর্বরী আহমেদ, শ্রাবন্তী নার্মিন আলি, জাভেদ জাহাঙ্গীর, আইমদী হোসেন। এঁদের অগ্রবর্তী নুজহাত মান্নান, রুমানা সিদ্দিক, রুবানা হক, লীমান সোবহান। আরও আগে আছেন আজফার হোসেন, আদিব খান। আর সত্তরের দশকে প্রচুর সম্ভাবনা জাগিয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন কবি ফিরোজ আহমদউদ্দিন। নিয়াজ জামান সেই ষাট-সত্তর থেকে লিখছেন, গল্পগ্রন্থ সম্পাদনা করছেন, প্রকাশনা সংস্থা দিয়েছেন ইংরেজি লেখালেখিকে উৎসাহ দিতে। একইভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউপিএল প্রকাশনীর। আর ২০১৪ সালে এসে জিয়া হায়দার রহমানের উপন্যাস ইন দ্য লাইট অব হোয়াট উই নো তো সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিল। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।
সামান্য পরিসরে একটি বড় বিষয় নিয়ে লেখাটা কষ্টকর। অনেক কথা না বলা থেকে যায়, অনেক নাম বাদ পড়ে যায়। তা থাকুক অথবা পড়ুক। মোট যে কথা তা হলো, ইংরেজি লেখালেখি বাংলাদেশকেই ধারণ করছে, এই সময়কেই পুনঃকল্পনা করছে, নতুন বাংলাদেশকে উপজীব্য করছে, তারুণ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এটি পৌঁছে যাচ্ছে সারা পৃথিবীর বাঙালি তরুণদের কাছে, নতুন তথ্য ও কম্পিউটার প্রযুক্তির কারণে। এসব তরুণ এই লেখালেখি পড়ে নতুন করে দেশকে চিনছে, ভালোবাসছে।
