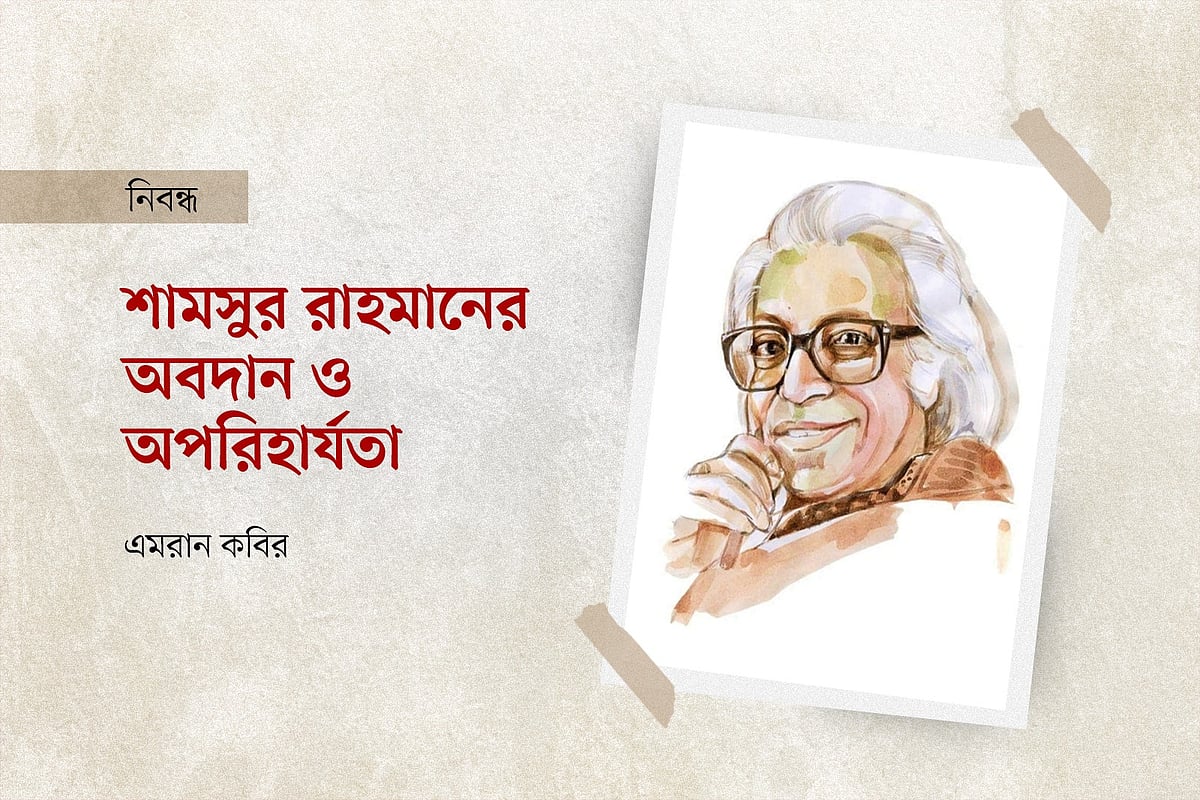কেন শামসুর রাহমান গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ কবিদের মধ্যে প্রায়ই উচ্চারিত হয়। দ্বিধা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে তাঁরা অনেকেই মনে করেন, শামসুর রাহমান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নন। তাঁদের কাব্যধারা বিকাশে শামসুর রাহমানের কবিতা খুব একটা ভূমিকা রাখবে না।
কবিতার কাছে আমরা কী চাই? আর কবিতাকে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করি—এই দুই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শামসুর রাহমান–সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ উত্তর।
সেসব উত্তরের শুলুক সন্ধান করতে গেলে যেতে হবে বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসের কাছে। আমরা আপাতত অত বিস্তৃত সময়ের দিকে যাচ্ছি না। অন্তত গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের কাব্যপ্রবণতা আর কবিতা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর দিলেও আমরা এর উত্তর পেয়ে যাব। আর বলার অপেক্ষা রাখে না, ওই সময়টা কিন্তু তার আগের হাজার বছরেরই কবিতার ধারাবাহিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাস।
ওই সময়ে এসে কবিতা একাধিক ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে রবীন্দ্রাধিপত্যের বিপরীতে ফ্যাশনেবল রবীন্দ্রবিরোধিতা বনাম রবীন্দ্রানুকরণ; অন্যদিকে পশ্চিমা কাব্যপ্রবণতার প্রভাবে বদলে যেতে থাকা আমাদের আবহমান বংলা কবিতা। একদিকে ঐতিহ্য ধরে রাখার শিকড়সংলগ্নতা, অন্যদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্পৃহা জাগ্রত করার উপাদান হিসেব কবিতার ব্যবহার। ইউরোপ–শাসিত এই পরাধীন ভূখণ্ডে তখন হেজেমনির মতো ইউরোপীয় কবিতার আধিপত্য বা আভিজাত্যের প্রভাব; অন্যদিকে এই উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবাদী স্পৃহাকে দমিয়ে রাখার জন্য আধুনিকতার নামে উচ্চকিত কবিতার বিরোধিতা ছিল জীবনানন্দের ‘কবিতা নানারকম’–নামীয় সংজ্ঞার বিস্তার।
শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি পত্রপত্রিকায় লিখে পরিচিতি পেয়ে যান; এবং এই নামকরণের মাধ্যমেই তিনি উজ্জ্বলতরভাবে নিজেকে আলাদা করিয়ে নেন ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতা থেকে। এমনকি তাঁর সময় থেকেও। জীবন ও স্বপ্নের, বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম দেখালেন মানসমৃত্যু আর শারীরিক মৃত্যুর পার্থক্য।
এসব উপাদানের প্রভাবে বাংলা কবিতা তখন কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রানুকরণে অনেক কবিরই তখন সবার অজ্ঞাতে সমাধি হয়ে যায়। রবীন্দ্রবিরোধিতায় মগ্ন হয়ে বুদ্ধদেব বসুরা তখন নতুন কবিতার ইশতেহার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। সেখানে অন্তস্থ উপাদান আর বাহ্যিক কাঠামোর বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসক ইউরোপীয় আধুনিকতার নামে আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যক্তির একান্ত অনায়াস উপলব্ধিকে মুখ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চকিত কাব্যধারাকে অনাধুনিক বলে প্রচার করে। এতসব ডামাডোলের ভেতরে সবকিছু উপেক্ষা করে একাই একক বৈশিষ্ট্যে অনড় থেকে কাব্য রচনা করতে থাকেন কাজী নজরুল ইসলাম। আর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একদল তরুণ কবি ইউরোপের ওই ভাবধারাকে বাংলা কবিতায় নিয়ে এলেন। তাঁরা ভাবলেন, এভাবে বাংলা কবিতা আধুনিকীকরণের শুদ্ধতায় পরিশুদ্ধ হবে। নজরুল কারও কথা শুনলেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন, তিনি চির আধুনিক। এসবের বাইরে পঞ্চপাণ্ডব বলে খ্যাত কবিরা বাংলা কবিতায় অনায়াস–নমনীয় ভাষা তৈরি করলেন বটে; কিন্তু এমন সব আন্তর্জাতিকতা ঢুকে পড়ল, এত সব আড়াল ঢুকে পড়ল, যা বাংলা কবিতাকে নিয়ে গেল সাধারণ্য থেকে দূরে।
বলার অপেক্ষা রাখে না পরবর্তী সময়ে এই ধারা চলতে থাকল চল্লিশের দশক থেকেই। শামসুর রাহমান তো সেই ধারারই এক সংযোজন এবং কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একজন আমৃত্য সারথি।
সেই পুরোনো প্রশ্ন—শামসুর রাহমানের এখানে বিশিষ্টতা কী, যেখানে ব্যক্তির আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে বৃহত্তর জীবনের প্রতিধ্বনিকে অনুপস্থিত রাখার কৌশল নিয়ে পুরো বাংলা কবিতাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ভূখণ্ডে? এককথায় যদি উত্তর দিই, তাহলে বলতে হবে, অন্যরা যেখানে অন্য অনেক উপাদানের সঙ্গে (এবং বিচ্ছিন্নভাবে) আবেগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, শামসুর রাহমান সেখানে বৃহত্তর জীবন ও স্বদেশের প্রতিধ্বনির সঙ্গে নিজের পুরো কাব্যযাত্রাকে মিশিয়েছেন। এককথার উত্তরের পরে এই কথার ব্যাখ্যার জন্য বহুকথা বলার দরকার। আমরা এখন সেদিকেই যাব।
তিরিশি আধুনিকতা যেখানে ভিখারির মতো হাত পেতেছে কিটসের কাছে, ইয়েটসের কাছে, গ্রিক ও পাশ্চাত্য পুরাণের দ্বারে দ্বারে, মালার্মের পরাবাস্তব বৈঠকিতে; বোদলেয়ারের বিকল্প জগতে, র্যাবোর অপরাধী নরকে। শামসুর রাহমান সেখানে হেঁটেছেন আপন নগরীতে। এ নগরীর বাতাসে সেরেছেন ‘রুপালি স্নান’। ঢাকাকে ঢাকা হয়ে উঠতে দেখে তাকে আপন করে নিয়েছেন। কখনো তাঁর মনে হয়নি নরক বা বিকল্প জগৎ।
শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি পত্রপত্রিকায় লিখে পরিচিতি পেয়ে যান; এবং এই নামকরণের মাধ্যমেই তিনি উজ্জ্বলতরভাবে নিজেকে আলাদা করিয়ে নেন ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতা থেকে। এমনকি তাঁর সময় থেকেও। জীবন ও স্বপ্নের, বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম দেখালেন মানসমৃত্যু আর শারীরিক মৃত্যুর পার্থক্য। বিংশ শতাব্দীতে ত্রিশের আলোড়নের পর এমন ভাবধারা ছিল একেবারেই নতুন। ‘রৌদ্র করোটিতে’ তিনি উজ্জ্বলতর করলেন সবকিছু। আঁধার ও অবগুণ্ঠন বিদায় করলেন। তাঁর চেতনাকে খোলাসা করলেন। বুদ্ধদেব বসুর ‘প্রান্তরে কিছুই নেই: জানালার পর্দা টেনে দে’র বিপরীতে তিনি রোদের আলোকে নিয়ে এলেন তাঁর কবিতার করোটি। বুদ্ধদেব বসুর ওই চরণ নিছক তাঁর চরণ নয়, তাঁর নিজস্ব কাব্যচেতনা, এমনকি তিরিশি কাব্যপ্রবণতারও কেন্দ্র। শামসুর রাহমান ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’তে যে নানা ধরনের মৃত্যুর মধ্যে রেখা টেনে টেনে দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় কাব্য ‘রৌদ্র করোটিতে’ এসে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিরিশির বিপরীতে স্বতন্ত্র হয়ে। এই স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বলতর হয়েছে ‘বিধ্বস্ত নীলিমা’য় তারপর ‘নিরালোকে দিব্যরথ’, এরপর ‘নিজ বাসভূমে’।
তিরিশি আধুনিকতা যেখানে ভিখারির মতো হাত পেতেছে কিটসের কাছে, ইয়েটসের কাছে, গ্রিক ও পাশ্চাত্য পুরাণের দ্বারে দ্বারে, মালার্মের পরাবাস্তব বৈঠকিতে; বোদলেয়ারের বিকল্প জগতে, র্যাবোর অপরাধী নরকে। শামসুর রাহমান সেখানে হেঁটেছেন আপন নগরীতে। এ নগরীর বাতাসে সেরেছেন ‘রুপালি স্নান’। ঢাকাকে ঢাকা হয়ে উঠতে দেখে তাকে আপন করে নিয়েছেন। কখনো তাঁর মনে হয়নি নরক বা বিকল্প জগৎ। এ শহরেই তিনি ঝাঁজালো মিছিলের অংশ হয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন জাতীয়তাবাদী চেতনায়, স্বাধিকারের উদ্দেশে। কখনো মনে হয়নি তাঁর যে জানালা বন্ধ করতে হবে। মনে হয়েছে, এ তো আমার।
‘নিজ বাসভূমে’ থেকে কবির এক আত্মনিবেদন ও বিবর্তন লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যযাত্রার দিকে তাকালে দেখা যায় দুই ধারারই বেগবান রূপ। বলা যায়, এই কাব্য তাঁর কবিতার বাঁকবদলের এক সন্ধিতে দাঁড়িয়ে। একদিকে রয়েছে ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’, ‘ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯’, ‘পুলিশ রিপোর্ট’, ‘হরতাল’, ‘আসাদের শার্ট’। অন্যদিকে রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি, কবিয়াল রমেশ শীল ইত্যাদি। প্রথম অংশে স্বদেশিকতাকে এমন তীব্র আবেদনময়রূপে উপস্থাপন করেছেন, যার শিল্পরূপ ও আবেগ এখনো তরতাজা। ‘আসাদের শার্ট ’এখনো আমাদের প্রাণের পতাকা। যে রক্তমাখা শার্ট ছিল পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে দেহান্তরিত এক ব্যক্তির নিতান্তই পরিচ্ছদ, শামসুর রাহমান তাঁকে রূপ দিলেন প্রাণের পতাকায়। আপামর জনসাধারণও তা গ্রহণ করে নিল পরম মমতায়। যা আজও নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বল করছে। যুদ্ধের আগুন যখন লাগে, তখন শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় এভাবে ফাগুনের আবাহন করেছেন। তা আজও জাগরূক আমাদের জাগরণে, আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মননে, আমাদের আদর্শে। ‘বর্ণমালা’, ‘আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’য় যে আত্মপরিচয়ের উদ্ভাস, তা–ই আমাদের একসময় স্বাধীন হওয়ায় ব্রতী করেছে। তাঁর কাব্যযাত্রার অন্য অংশে রয়েছে ব্যক্তির একান্ত ভূভাগ। রয়েছে প্রেম, ব্যর্থতা, আবেগ; যেখানে ঝাঁজালো মিছিল নেই।
শামসুর রাহমানের এই কাব্য থেকে যে পৃথক দুই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবিতার ধারা দেখতে পাওয়া যায়, দিনে দিনে তা-ই পুষ্ট হয়েছে এবং কবিকে করেছে স্বতন্ত্র। জীবনের শেষাবধি তিনি এই দুই ধারায় ব্রতী ছিলেন। এই দুই ধারার সম্মিলিত রূপ–কাঠামো-বৈশিষ্ট৵-বিন্যাস-বক্তব্য-অভিব্যক্তি যা নির্দেশ করে, শামসুর রাহমান আদতে তা–ই।
এই ধারার এক প্রধান ও নিরঙ্কুশ কাব৵ ‘বন্দী শিবির থেকে’। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অবরুদ্ধ ব্যক্তি শামসুর রাহমান যোদ্ধা না হয়ে কবিই থেকে গেলেন। ১৪টি কবিতা রচনা করেন তিনি এ সময়। পুকুরপাড়ে গাছের নিচে বসে এ সময় যে দুটি কবিতা রচনা করেন, ‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’ তা বাংলাদেশের ইতিহাস ও বাংলা কবিতার ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে থাকল। স্বাধীনতার স্বরূপ ও অনুভূতি, সংগ্রামের পথ ও পাথেয়, অর্জনের উপলব্ধি ও আত্মত্যাগ, সর্বোপরি সামগ্রিক যে উদ্দীপনা ও লক্ষণ, তা শিল্পিত হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ধারাবাহিক আত্মত্যাগ ও নির্যাতন, তা উঠে আসে সংগ্রামের পরম্পরায়।
বাংলাদেশের যত উল্লেখযোগ্য অর্জন ও ঋণাত্বক পরিবর্তনের দুর্বৃত্তপনা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রতিটির অনুপুঙ্খ কাব্য-ভাষ্য উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়, যা স্পষ্টতই নিরঙ্কুশভাবে অন্য কারও কবিতায় আসেনি। ‘দুঃসময়ের মুখোমুখী’ থেকে তাঁর শেষতম কাব্যের মধ্যে এই কাব্যভাষ্য উপস্থিত। ‘দুঃসময়ের মুখোমুখী’তে উঠে এসেছে স্বাধীনতা–উত্তর দুঃসহ চালচিত্র।
বাংলাদেশের যত উল্লেখযোগ্য অর্জন ও ঋণাত্বক পরিবর্তনের দুর্বৃত্তপনা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রতিটির অনুপুঙ্খ কাব্য-ভাষ্য উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়, যা স্পষ্টতই নিরঙ্কুশভাবে অন্য কারও কবিতায় আসেনি। ‘দুঃসময়ের মুখোমুখী’ থেকে তাঁর শেষতম কাব্যের মধ্যে এই কাব্যভাষ্য উপস্থিত। ‘দুঃসময়ের মুখোমুখী’তে উঠে এসেছে স্বাধীনতা–উত্তর দুঃসহ চালচিত্র। নিহত আগামেমনের চরিত্রের রূপকে তিনি গেয়েছেন ইলেকট্রার গান। ‘জয়নুলী কাকের’ মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অর্থনৈতিক শোচনীয়তার চিত্র। সামরিক শাসন নিয়ে লিখলেন ‘ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা’। তথাকথিত ইসলামীকরণের নামে এ দেশে মরুভূমির প্রাণী উট নিয়ে এলে বাংলার মানুষ দেখল মূর্খ-ধর্মান্ধদের উটমূত্র সেবন। তিনি লিখলেন ‘অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’। স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নূর হোসেন নিজেকে জীবন্ত পোস্টার বানিয়ে ফেললে তাঁকে নিয়ে লিখলেন ‘বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়’। এগুলো তো বাংলাদেশের জীবনী।
অন্যদিকে শামসুর রাহমান এই ধারার বাইরে অন্য যে ধারা প্রবহমান রেখেছিলেন, তাঁর সমালোচকেরা সেই প্রয়াসকে নিতান্তই ‘অভ্যাস’ বলে অখ্যায়িত করেছেন। বলা হয়েছে ‘পুনরাবৃত্তিময়’; কিন্তু একটু স্থির ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালে দেখা যাবে তাঁর এসব কবিতার মধ্যে রয়েছে সময়ের অস্থিরতার চিত্র, উন্মত্ততার ভয়াল রূপ, আত্মপ্রক্ষেপণের পৌনঃপুনিক আলো, কালো সময়ের দুর্গন্ধ ও সুবাস, বাস্তব ও পরাবাস্তবতার হাত ধরাধরি করে চলা উচ্ছলতা ও উদ্বেলতা; আছে আটপৌরে জীবনকে অন্যভাবে তুলে ধরার অদ্ভুত শোভা ও কদর্য, রয়েছে নাগরিক মনোবিশ্বের রূপ-অরূপের খেলা।
কবি শামসুর রাহমানের কবিতার এই দুই ধারাকে যদি সমগ্রতা দেওয়া হয়, অর্থাৎ একত্র করে দেখা হয় এবং তিরিশের সূচনাবিন্দু ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিচার করি, কবিতার কাছে আমাদের যা চাওয়া, তা যদি বিবেচনায় ধরি, তাহলে মোটাদাগে বলতে হবে—‘আমাদের অস্তিত্বের ভেতরে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত অধিকার, তা শামসুর রাহমানের মতো করে আর কেউ বলেননি।’ শুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের চশমা দিয়ে তাঁর এই অবদানকে প্রত্যক্ষ করা যাবে না। যাবে ত্রিশের নানা হেজিমনিক বৈশিষ্ট্যকে উজিয়ে, উচ্চকণ্ঠ না হয়েও বৃহত্তর জনমানুষের একান্ত হতে পারা সাফল্যের ভেতরে। চাপিয়ে দেওয়া ইউরোপীয় ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ত্রিশকে ধারণ করে এবং ত্রিশকে উজিয়ে তিনি কবিতায় যে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য; এবং স্পষ্ট করে বলা যায়—এ ক্ষেত্রে তিনি বেশ একা।