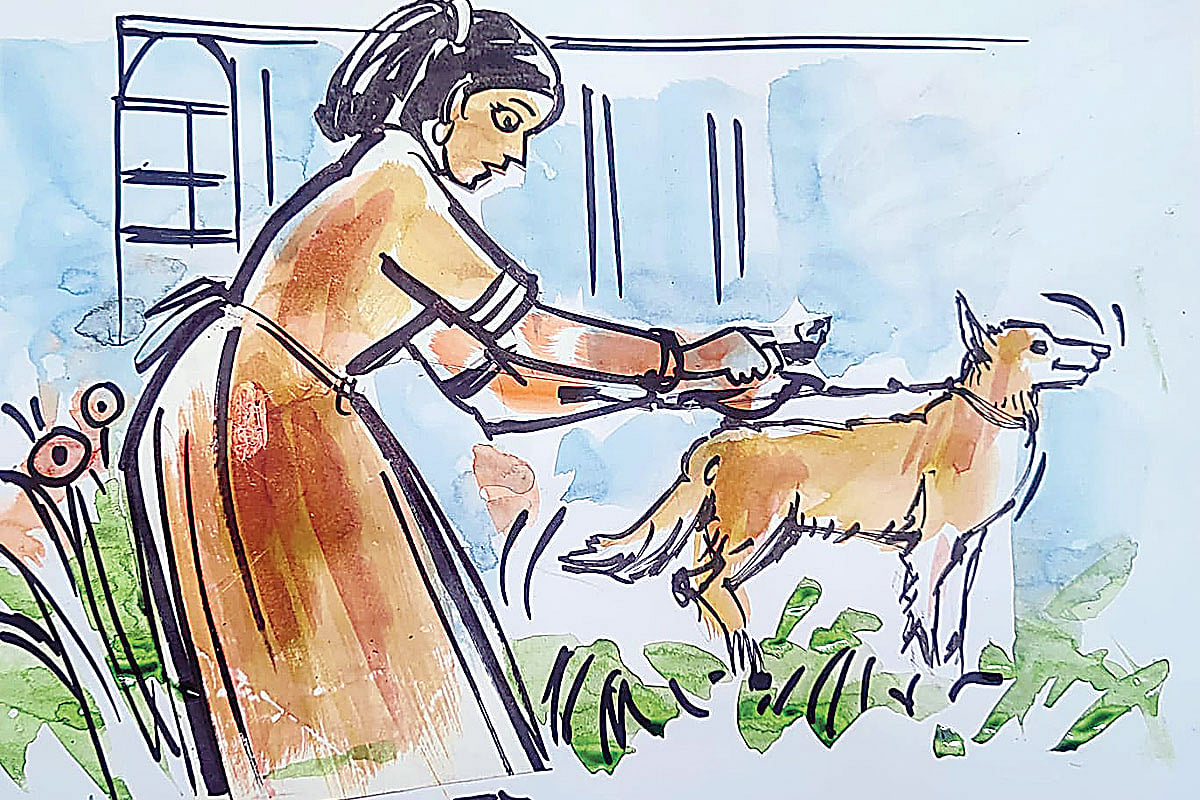
পাঠকের লেখা-৭৮
আমাদের স্পটি ও জেটি
প্রিয় পাঠক, প্রথম আলোয় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়: readers@prothomalo.com
১৯৫৪ সালে পুরান ঢাকার আলুবাজার এলাকা থেকে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন রোডের সামনে বেশ খানিকটা খালি জায়গাসহ তিন রুমের একটা বাড়িতে উঠি। চাকরির সুবাদে বাবা প্রতি মাসের একটা বড় সময় ঢাকার বাইরে থাকতেন। তাই আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি বাড়িতে একটা কুকুর পোষার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেশি কুকুর না রেখে তিনি একটা বিলেতি ল্যাব্রাডর কুকুর কিনে আনলেন। হালকা ঘিয়ে রঙের ওপর গাঢ় বাদামি ছোট–বড় ছোপ আর বাদামি রঙের লেজের কুকুরটিকে বাবা নাম দিলেন ‘স্পটি’। আমাদের সবার ওকে খুব পছন্দ হলো।
বাড়ির সামনের বড় গেটের এক পাশে একটা হাসনাহেনা, আরেক পাশে একটা স্থলপদ্মের বড় গাছ ছিল। তার পাশেই স্পটিকে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। সকাল থেকে আম্মা ওকে চার–পাঁচবার খাবার দিয়ে আসতেন। আম্মা ভুলে গেলে ক্ষুধা পেলে ঠিকই ডাকাডাকি শুরু করত। সপ্তাহে দুই–তিন দিন আম্মা ঠাটারীবাজারের কসাইয়ের দোকান থেকে মাংসের উচ্ছিষ্ট কিনে আনতেন। পরে সেগুলো চালের সঙ্গে হলুদ ও লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে স্পটির জন্য রেখে দিতেন। সেই রান্নার যে একটা ঘ্রাণ হতো, সেটা এখনো মনে হয় আমার নাকে ভেসে আসে।
স্পটিকে আম্মা কিছুদিন পরপর পশু হাসপাতালে নিয়ে ওর আঁচড়/কামড়ে যাতে কারও ক্ষতি না হয়, তার জন্য ইনজেকশন দিয়ে আনতেন। আর চামড়ায় পোকা না হওয়ার ওষুধ নিয়ে আসতেন।
আমরা ভাইবোনেরা প্রায়ই গেটের সামনে খেলাধুলা করতাম। একদিন আমি আমার ভাইকে খেলাচ্ছলে একটা ধাক্কা দিলে ও পড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে। স্পটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে আমার পায়ে খুব জোরে আঁচড় দেয়। আম্মা আমার পায়ের অবস্থা দেখে ডেটল দিয়ে মুছে শুয়ে থাকতে বললেন।
বিকেলে আমাদের পাড়ার ডাক্তার আলী আজগরের কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, পোষা কুকুর, আবার ওর ভ্যাকসিনও দেওয়া আছে, তাই কোনো রকম ভয় নেই। জলাতঙ্কের ইনজেকশনেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আম্মা তাতে স্বস্তি পেলেন না। বরং ডাক্তারকে বললেন, কমপক্ষে যে কয়টা ইনজেকশন দেওয়া দরকার তিনি যেন তার ব্যবস্থা করেন।
আমাকে মোট সাতটা ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধটা প্রবেশ করানোর সময় মনে হতো আমার চামড়া কেটে কেটে যাচ্ছে—খুব কষ্ট হতো। যেখানে সুচটা প্রবেশ করানো হতো, সেই জায়গায় একটা গোল চাকা হয়ে যেত। সবার সামনে আওয়াজ করে কাঁদতাম না, কিন্তু চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ত। স্পটির ওপর প্রথমে খুব রাগ হলেও পরে ওর সঙ্গে ঠিকই খেলতাম।
বাড়ির আশপাশে, বিশেষ করে রাতে কোনো অচেনা লোক ঘোরাঘুরি করলে স্পটি খুব চেঁচামেচি করত। সে রকমই এক রাতে ও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পর একেবারে চুপ হয়ে গেল। সকালে আম্মা দেখলেন, স্পটি অনেকটা রক্তের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে আছে। কোনো চোর ছুরি মেরে রেখে গিয়েছিল। বাড়িতে একটা শোকের আবহ তৈরি হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত এত কাছের কাউকে আমরা আগে হারিয়েছি বলে মনে হচ্ছিল না।
আমাদের সবার এ রকম মুষড়ে পড়া অবস্থা দেখে মাসখানেকের মধ্যে বাবা জার্মান শেফার্ড জাতের আরেকটা কুকুর নিয়ে এলেন। ওর গায়ের পশমগুলো স্পটির মতো ঘন ছিল না, বরং মসৃণ কাপড়ের মতো ছিল। গায়ের রং জেট ব্ল্যাক কালির মতো ছিল বলে বাবা ওর নাম দিলেন ‘জেটি’। যখনই বাবা ঢাকার বাইরে থেকে ফিরতেন, খুশিতে জেটির লেজ নাড়ানো আর বাবার আদর পাওয়ার অস্থিরতা দেখার মতো ছিল। বাবা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করার পর জেটি শান্ত হতো।
জেটিকে আনার তিন–চার বছরের মধ্যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ওই বাসা বদল করে তেজগাঁও এলাকায় চলে যেতে হয়। এর কিছুদিন আগে থেকেই জেটির চর্মরোগ দেখা দেয়। ওষুধ লাগানো আর ভালোভাবে পরিষ্কার করার পরও ওর শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসত। পশু হাসপাতাল থেকে কয়েকবার বিভিন্ন চিকিৎসা দেওয়ার পরও সেটা ভালো হচ্ছিল না।
আমাদের তেজগাঁওয়ের বাসায় তেমন খোলা জায়গা ছিল না। জেটির আশ্রয় হয়েছিল সিঁড়ির পাশে খুব ছোট জায়গায়। ওর চামড়ার ঘা, ওপরতলার অন্য ভাড়াটেদের আপত্তির কারণে জেটিকে আর সেখানে রাখা গেল না।
বাবা নিজে গাড়িতে করে জেটিকে ঢাকনা দেওয়া একটা বাক্সে করে পুরান ঢাকার কোথাও রেখে দিয়ে আসেন। কিন্তু জেটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক দিন পরই ফিরে এল।
শেষ পর্যন্ত বাবা ওকে গাড়িতে করে ফেরি পার হয়ে নদীর ওপারে ছেড়ে আসেন। বাসায় ফিরে আমাদের কাছে সে কথা বলতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বাবা চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, ‘মা, আমি তো তোমাদের কারও এ রকম অবস্থা হলে বুকে আগলে রাখতাম; কিন্তু অতি নিষ্ঠুরভাবে ওকে ফেলে আসতে বাধ্য হলাম।’