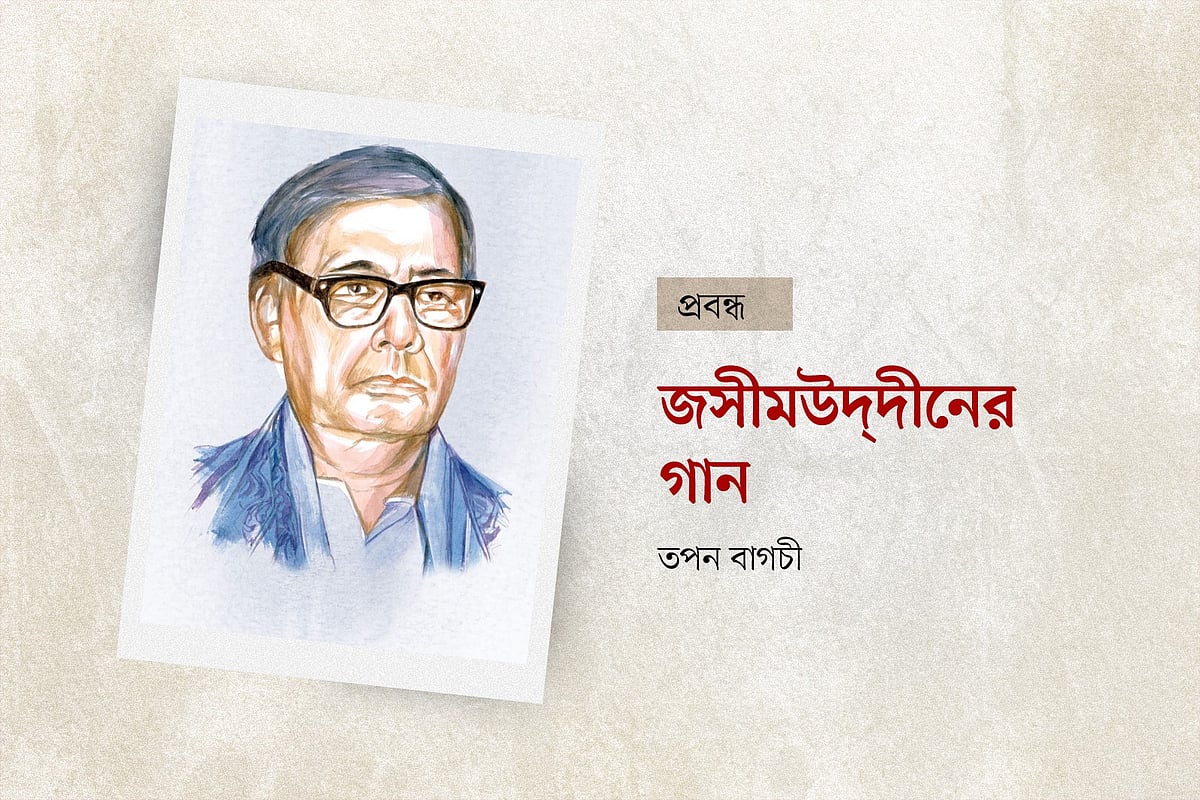জসীমউদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) কবিসত্তা ও গীতিকারসত্তা সমান্তরাল প্রবহমান। কবিতাগ্রন্থেই স্থান পেয়েছে তাঁর লেখা গান। অর্থাৎ গানের বাণীকে তিনি সচেতনভাবে কবিতার মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ ‘রাখালী’তে (১৯২৭) তাই সন্নিবিষ্ট ১৯টি কবিতার মধ্যে ৫টিই গান। নন্দলাল বসুর প্রচ্ছদে দীনেশচন্দ্র সেনকে উৎসর্গ করা এই গ্রন্থের সমালোচনায় ‘সওগাত’ পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) ‘সবগুলিই ভাল কবিতা’ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকা (কার্তিক ১৩৩৭) একে ‘কবিতাপুস্তক’ হিসেবে আলোচনা করেও এর ‘মেঠো সুর’ গেঁয়ো গন্ধ ও স্বভাবসুন্দর রূপকে ঠিকই চিহ্নিত করতে পেরেছে। মেয়েলি গানের সুরে রচিত ‘সিঁদুরের বেসাতি’ কবিতার উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে। তবে ‘রাখালী’ কবিতাগ্রন্থের গানের উপস্থিতি নিয়ে শংসাসূচক মন্তব্য করেন কবি-সমালোচক কালিদাস রায়। ‘সম্মিলনী’ পত্রিকায় (পৌষ, ১৩৩৬) তিনি লেখেন, ‘বঙ্গসাহিত্যে Pastoral Songs লেখার জন্য কুমুদরঞ্জনের খ্যাতি আছে। কবি কুমুদরঞ্জন রাঢ় দেশের লোক। রাঢ় দেশের রীতি-প্রকৃতি ও পল্লীজীবনটি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বেশ ফুটিয়াছে। জসীমউদ্দীনও Pastoral Songs লিখেছেন—রাখালিয়া সুরে। পুস্তকের নামও রাখালী।...জসীমউদ্দীনের রাখালিয়া গান পূর্ববঙ্গের নদীর চড়া হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে।। তাই ইহা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব সম্পদ।...রাখালিয়া ভাষাতেই যে-গানগুলি রচিত, সেগুলি আমার সবচেয়ে ভালো লাগিল।’
আমরা জানি, ‘রাখালী’ গ্রন্থে প্রকাশের আগেই জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতা মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। খুব আনন্দের সঙ্গে কালিদাস রায় জানিয়েছেন ‘আগামী বৎসর শিক্ষার্থীদেরকে “কবর” কবিতাটি পড়াইতেও হইবে।’ ‘রাখালী’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় কবিতা ‘সিঁদুরের বেসাতি’ই গান হিসেবে গাওয়ার জন্য রচিত। এর কাব্যগুণ বিবেচনা করে একে প্রথম কবিতাগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার মর্যাদা দিয়েছেন।
কবিতাগ্রন্থেই স্থান পেয়েছে তাঁর লেখা গান। অর্থাৎ গানের বাণীকে তিনি সচেতনভাবে কবিতার মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ ‘রাখালী’তে (১৯২৭) তাই সন্নিবিষ্ট ১৯টি কবিতার মধ্যে ৫টিই গান। এই গ্রন্থের সমালোচনায় ‘সওগাত’ পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) ‘সবগুলিই ভাল কবিতা’ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
‘সিঁদুরের বেসাতি’ কবিতাটি মাসিক ‘কল্লোল’ পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। শিরোনামের সঙ্গে লেখা ছিল ‘মেয়েলি গানের সুর’ কথাটি। গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণের পাঠে আমরা পাই ‘বেনে’ ও ‘কন্যা’র দ্বৈত কথোপকথন আকারে এটি মুদ্রিত; কিন্তু পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রথম প্রকাশের সময় কথোপকথনের এই আঙ্গিকে ছিল না। আবার এই গান ‘রঙিলা নায়ের মাঝি’ (১৯৩৫) গ্রন্থে ছাপা হয় ‘রূপক নাটিকা’ হিসেবে।
এক বেনে গ্রামে যায় শাঁখা, সিঁদুর, পুঁতির মালা, গলার হার, নাকের নথ বিক্রি করতে। আর কন্যা তার মায়ের কাছ থেকে এক ধামা ধান নিয়ে যায় বেনের দোকানে পুঁতির মালা কিনতে। বেনে সেই গ্রাম্য কন্যার সরলতার সুযোগে ‘হাসি মুখ আর খুশি বুক’-এর বিনিময়ে হাতে শাঁখা, নাকের নথ ও কপালে সিন্দুর পরিয়ে দেয়।
কন্যা
শোনো শোনো বানিয়ারে কই তোমার আগে
তোমারও না নথ ও শাঁখা কত দাম লাগে?
বেনে
আমার না শাঁখা লইতে লাগে হাসি মুখ,
আমার না নথ লইতে লাগে খুশি বুক।
কন্যা
নিলাম নিলাম নথও নিলাম, নিলাম তোমার শাঁখা
তোমার কথা বানিয়ারে, হৃদে রইল আঁকা।
সিঁদুর আগেই নেওয়া হয়েছে। শাঁখা-সিঁদুর-নথ দিয়ে বেনে তো কন্যাকে সনাতন ধর্মীয় রীতিতে মানবিক বন্ধনে আকৃষ্ট করেছে। তাই কন্যার উপলব্ধি—
ওই বিদেশি বানিয়া মোরে পাগল কইরা গেছে
আমার মন কাড়িয়া নেছে রে সজনী!
শাঁখা না কিনিতে আমি হাতে বান্ধলাম ডোর
সিঁথির সিন্দুর কিনে চক্ষে দেখি ঘোর।
নথ না কিনিয়া আমি পথে করনু বাসা
একেলা কাঁদিয়া ফিরি লয়ে তারি আশা।
এই যে মেয়েলি গানের সুরে রচিত কবিতা। সুর শোনার আগের পাঠেও আমরা মুগ্ধ হতে পারি তার চিত্রকল্পের শক্তিতে। বেনে বলছে—
সাঁঝের কোলে মেঘরে, তাতে রঙের চূড়া,
সেই মেঘে ঘষিয়া সিন্দুর করছি গুঁড়া।
সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ সূর্য ডোবার আগে যে রক্তিম আভা বা রঙের চূড়া, সেই সময়ের লাল মেঘের সঙ্গে ঘষে সিন্দুরকে গুঁড়া করা হয়েছে। কী অপূর্ব চিত্রকল্প!
কপালের শোভা বাড়ায় যে সিন্দুর, তাকে দেখতে কেমন লাগে? ‘তোমার রাঙা ঠোঁটের মতো দেখতে মনোলোভা’। রাঙা ঠোঁটের মতো দেখতে সুন্দর সেই সিন্দুর। উপমার চমৎকারিত্ব এখানে গানের কথাকেও কাব্যিক করে তুলেছে। শাঁখা কিনতে বা সিন্দুর কিনতে কত দাম লাগে তা জানতে চাওয়ায় বেনে বলে, এর দাম হচ্ছে ‘হাসি মুখ’ আর ‘খুশি বুক’। অর্থাৎ মুখের হাসি আর বুকের খুশির বিনিময়ে বেনে তার সওদা বিক্রি করতে চায়। এখানেও হাসি-খুশির মতো মনোজাগতিক উপলব্ধিকে দাম অর্থমূল্যের বিপরীতে স্থাপন করার মধ্যে যে কবিত্ব তা তুলনারহিত।
‘রাখালী’র চতুর্থ কবিতা ‘বৈদেশি বন্ধু’ হলে দ্বিতীয় গান। ‘গান-বারোমাসির সুরে’ বলা না থাকলে একে কবিতা হিসেবেই মনে করা যেত। গানের প্রচলিত কাঠামোর মতো, অস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী, আভোগ নেই−কবিতার মতো প্রবহমান। সুরেই কেবল এর সাংগীতিক অবস্থান ধরা পড়বে।
‘কবি তাহার এই পল্লী কাব্যখানিকে আগাগোড়া পল্লীর ভাষায়ই রচনা করিয়াছেন। পল্লীর ধানে-ঢাকা, জলে ভাষা, গাছে-ছাওয়া সুন্দর দৃশ্যটি এই কাব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাঝ মাঝে দুই চারটি মুর্শীদ্যা গান, জারি গান, ভাটিয়ালী গান সংযুক্ত করিয়া কবি কাব্যখানার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।’
বিদেশি বন্ধু মা-বোনের কাছে ফিরে যাবে, সেই বিরহ সৃষ্টি হয় অভাগী অবলার মনে। সেই বিরহের সুরই ধ্বনিত হয়েছে এই গীতিকবিতায়। বৈদেশি বন্ধু এসেছিল ‘অভাগী অবলার’ বাড়িতে ধান কাটতে। এই কিষানবন্ধুর প্রেমে পড়ে যায়। ধান কাটতে এসে মন কেটে যায়—
‘আমার দেশে ধান কাটিতে মন কাটিয়া গেলে,
ধানের দামই নিয়ে গেলে মনের দামটা ফেলে।’
এই যে ‘মনের দাম’ বা ‘মন কাটা’—এ রকম রূপকের মাধ্যমে তিনি বিরহিণীর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।
পরবর্তী গানটির নাম ‘সুজন বন্ধুরে’। এর পরিচয় গান এবং সুর ‘বন্ধের গানের সুর’ বলা হয়েছে। এটি পাঁচ অন্তরার গান—
‘ও সুজন বন্ধুরে
আমার যাবার বেলায় নয়ন-জলখানি,
যদি তোমার মনে না লয় আমি
না য্যান জানি।’
এই গানে ‘ব্যথার মলো’, ‘ফুলের সাথী’, ‘চেকন সুর’ প্রভৃতি শব্দবন্ধ কাব্যরূপে বিশেষায়িত। ভালো লাগার কথা কবি গোপন রাখতে চান, তাই গেয়ে ওঠেন—
‘বন্ধু গো, ভালো লাগে বইলা আমি চাই যে মুখের পানে
যদিও তুমি না চাও ইহা লোকে না য্যান জানে;
—রে পরান বন্ধু।’
গোপনতাই যে প্রেমের সৌন্দর্য, সে কথাটি ফুটে উঠেছে এই গানে। তবে নদীর এক কূলের জন্য অন্য কূলের কান্না ফুটে উঠেছে আরেক অন্তরায়—
‘তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে বহে নদী
ও কূলের লাগিয়া এ কূল কান্দে নিরবধি।’
শুধু নদীর কূল কান্দে, তা–ই নয়, দুটি চিকন সুরের কান্নাও কবি শুনতে পান। এই যে সমাসোক্তি অলংকার, তার প্রয়োগে এই গান হয়ে ওঠে কাম্যময়।
‘তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে বেশম দূর,
দুই ধারে কান্দিয়া ফেরে দুইটি চেকন সুর।’
এরপর ঘাটুগানের সুরে জসীমউদ্দীন লিখেছেন ‘মনই যদি নিবি’ নামের গানের কবিতা—
মনই যদি নিবি কেন মন করিলি খালি
কাঞ্চা বাঁশে আগুন দিয়ে বাড়ালি ধুঁয়ালিরে।
—রে পরান বন্ধু!
এই গানে ‘কাঞ্চা বাঁশ’, ‘জালি কুমড়া’ ‘অফুট নালের কুঁড়ি, ‘বুকের আগুন’ প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহারে গানটি সমৃদ্ধ হয়েছে।
‘ফুলই যদি নিবি রে বন্ধু, ভাঙলি কেন বোঁটা
জালি কুমড়া ছিঁড়ে কেন করলি জাতের খোঁটারে।
এই অন্তরায় চমৎকার এই জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। ফুল নিতে চাইলে বোঁটা ছেঁড়া ঠিক নয় অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছাতে চাইলে পথের কোনো অংশ নষ্ট করা যাবে না।
জালি কুমড়া ছিঁড়ে তো পাকা কুমড়া পাওয়ার পথ নষ্ট করা যাবে না। এখানে জালি কুমড়া তো অপরিণত বয়সের প্রতীক। ফুলও পরিণত জীবনের প্রতীক। এরপর ‘গহীন গাঙ্গের নায়া’ নামের ভাটিয়ালি সুরের গানটি তো এখনো সমান জনপ্রিয়—
‘আমার গহীন গাঙ্গের নায়া।
(ও তুমি) অফর বেলায় নাও বাইয়া যাওরে
(ওরে ওরে ও দোরদি) কার পানে বা চায়া।’
এই গানে ‘ভাটির দ্যাশের কাজল মায়া’, পরান কেঁদে বেড়ানো, মেঘের হাতছানি দেওয়া প্রভৃতি অনুষঙ্গে অঙ্কিত চিত্রকল্প সাধারণ কবিতাকে হার মানায়। কবি লিখেছেন—
কইও খবর তাহার লাইগ্যা
কাইন্দা মরে এক অভাইগ্যারে
(ও তার) ব্যথার দেওয়া থাইক্যা থাইক্যা
ঝরে নয়ন বায়ারে।
আমার গহীন গাঙ্গের নায়া।
এই যে ব্যথার মেঘ চোখ বেয়ে ঝরার ভেতর দিয়ে যে চিত্রকল্পের আভাস পাই, তা নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর।
জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত কাব্য হলো ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ (১৯২৯)। সওগাত পত্রিকার (আশ্বিন ১৩৩৬) সমালোচনায় লিখেছিল, ‘কবি তাহার এই পল্লী কাব্যখানিকে আগাগোড়া পল্লীর ভাষায়ই রচনা করিয়াছেন। পল্লীর ধানে-ঢাকা, জলে ভাষা, গাছে-ছাওয়া সুন্দর দৃশ্যটি এই কাব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাঝ মাঝে দুই চারটি মুর্শীদ্যা গান, জারি গান, ভাটিয়ালী গান সংযুক্ত করিয়া কবি কাব্যখানার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।’
গ্রন্থের ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন, এই গ্রন্থের গানগুলো বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বাঙালির লোকসংগীতকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবেশনে জসীমউদ্দীনের কৃতিত্বের সমান কাউকে পাওয়া যাবে না। এসব গানের কাব্যমূল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই এ রকম উচ্চতর মূল্যায়নে গ্রহণ করেছেন।
আমাদের আগ্রহ এই গানগুলোর প্রতি। যদিও গোটা কাব্যকেই ড. দীনেশচন্দ্র সেন সংগীতের পর্যায়ভুক্ত বলে প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘জসীমউদ্দীনের এই বইখানি ছোট হইলেও ইহা একখানি কাব্য, ইহার উপদান বাঙ্গালীর চিরাভ্যস্ত গীতিকবিতার কতকগুলি সুর ও ছন্দ, কিন্তু নানা সুর একত্র করিয়া একটি বড় রাগিণী সৃষ্টি করার শিক্ষা-শক্তি ইহার আছে।’ (বিচিত্রা, বৈশাখী ১৩৩৯)
‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ শুরুই হয়েছে রাখালী গানের উদ্ধৃতি দিয়ে—
‘বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল পাঙ্খা দেয় নাই বিধি।’
মোট ১৪টি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে ১৪টি গ্রাম্য গানে বা গানের অস্থায়ী অংশ যুক্ত হয়েছে—
এক.
বাড়ি আমার বাড়ি
বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাঙ্খা দেয় নাই বিধি।
— রাখালী গান
দুই.
এক কালা দাঁতের কালি, যা দ্যা কলম লেখি
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈন্য দেখি,
—ও কালা, ঘরে রইতে দিলি না আমারে
— মুর্শীদা গান
তিন.
চন্দনের বিন্দু বিন্দু কাজলের ফোঁটা
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর ছটা
— মুর্শীদা গান
চার.
কান্য দেয়া রে, তুই না আমার ভাই
আরো ফুটিক ‘ডলক দে’ চিনার ভাত খাই।
— মেঘ রাজার গান
পাঁচ.
লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন
— ময়মনসিংহ গীতিকা
ছয়.
ও তুই ঘরে রইতে দিলি না আমারে।
— রাখালী গান
সাত.
ঘটক চলিল চলিল সূর্য সিংহের বাড়িরে
— আসমান সিংহের গান
আট.
‘কি কর দুল্যাপের মালো; বিভাবনায় বসিয়া,
আসতাছে বেটীর দামান ফুল পাগড়ি উড়ায়া নারে।’
‘আসুক আসুক বেটির দামান কিছু চিন্তা নাইরে,
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি কামরাঙা পাটি মারে।
সেই ঘরেতে নাগায়া খুইছি মোমের সস্র বাতি,
বাইর বাড়ি বান্দিয়া থুইছি গজমতি হাতি নারে ।’
— মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান
নয়.
মৎস্য চেয়ে গহীন গম্ভ, পক্ষি চেনে ডাল
মায় সে জানে বিটার দরদ যার কলিজার শ্যাল।
নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।
— গাজীর গান
দশ.
বড় ঘর বান্দাছাও মোনা ভাই, বড় করছাও আশা
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খি ছাড়বে বাসা।
— মুর্শীদা গান
এগারো.
সাজ সাজ বলিয়ারে শহরে পৈল সাড়া
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া।
— মহররমের জারী
বারো.
রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে
বেলা গেল সন্ধ্যা হইল−ও হইলরে গৃহে জ্বালাও বাতি
না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাতিরে।
— রাখালী গান
তেরো.
বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধুরে
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা;
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশেরে।
— রাখালী গান
চৌদ্দ.
উইড়া যায় রে হংস পঙ্খি পইড়া রয়রে ছাল
দেশের মানুষ দেশে যাইব−কে করিব মায়া।
— মুর্শীদা গান
গ্রন্থের ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন, এই গ্রন্থের গানগুলো বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ গানগুলো কবির লেখা নয়। কিন্তু কবির গ্রন্থে রয়েছে বলে ভূমিকার স্বীকারোক্তি না দেখে অনেক গায়ক এগুলোকে জসীমউদ্দীনের লেখা গান বলে পরিচয় দিয়ে নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দেন। নিজের কাব্যের প্রতিটি সর্গের শুরুতে যে সকল চরণ তিনি শিরোধার্য করেছেন, তার পূর্ণরূপ সংকলিত গ্রন্থসমূহে স্থান দিয়েছেন। বাঙালির লোকসংগীতকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবেশনে জসীমউদ্দীনের একক কৃতিত্বের সমান কাউকে পাওয়া যাবে না। তিনি এসব গানের কাব্যমূল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই এ রকম উচ্চতর মূল্যায়নে গ্রহণ করেছেন।
আধুনিক গানের আঙ্গিক পুরোপুরি মান্য করেছেন কবি। পল্লিগানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঞ্চারী থাকে না। ঢালাওভাবে তিনি চার-পাঁচ-ছয় অন্তরা একই রকম জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার পল্লিগীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জসীমউদ্দীন আধুনিক গান লিখতে এসে নিজেকে সম্পূর্ণ আধুনিকায়ন করেছেন।
‘বালুচর’ (১৯৩০) কাব্যের ‘বাঁশরী আমার’ কবিতাটি ‘বংশী-হারা’ নামে ‘কল্লোল’ পত্রিকায় (মাঘ ১৩৩৩) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে শিরোনাম ছাড়াই কাব্যের সূচনা কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হয়। পরে এটি ‘বাঁশরী আমার’ নাম ধারণ করে। এটি মূলত গান। এই গানে চারটি তুকই বর্তমান। গানটির বিষয় বালুচরে রাখালের বাঁশি হারানোর বেদনা। এই বাঁশি কেবল বাঁশের বাঁশি নয়, রাখালের মূল সম্পদ। তাই গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে প্রথম অন্তরায়—
কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া (৬+৬)
চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া (৬+৬)
চলিতে চরণ ওঠে না বাজিয়া (৬+৬)
তেমন করে, (৫)
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে (৬+৬)
বালুর চরে। (৫)
এই গানে সঞ্চারী এবং আভোগ রয়েছে। সঞ্চারীতে ‘বাঁশের হিয়ায় রঙিয়া উঠেছে গোখুর-বেণু’ বলে গোধূলির বিবরণ চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আবার আভোগে সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে কাঁদিয়া মরে বলে যে সমাসোক্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা অনন্য কবিত্বের লক্ষ্মণ। গানের ক্ষেত্রে এই সময়ের আধুনিক কবিরাও যেখানে ছন্দ-অন্ত্যমিল ঠিক রাখতে পারেন না, সেখানে জসীমউদ্দীন যথাযথ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মাত্রাবৃত্তে ৬ মাত্রার পূর্ণপর্ব এবং ৫ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে সাজিয়েছেন। এই গ্রন্থের ‘প্রতিদান’ কবিতাটিও গান—
‘আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর
যে মোরে করিল পথের বিবাগী
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর॥’
‘বালুঘর’ কাব্যের আরও একটি গান রয়েছে ‘সন্ধ্যা’ নামে। জসীমউদ্দীন যে ধরনের পল্লিগীতি রচনা করেছেন, ইতিপূর্বে যার নিদর্শন পেয়েছি, এ গান তার থেকে আলাদা। এ গান একবারেই আধুনিক গান। পঞ্চকবির গানের যে ধারা, তারই সকল নিদর্শন এই গান—
‘আরো ক্ষণকাল দাঁড়াও সন্ধ্যা
মৃদু মন্থর পায়ে,
তারার মানিক জ্বালাব তোমার,
আঁধার আঁচল ছায়ে।’
এই হচ্ছে আস্থায়ী। সন্ধ্যাকে মৃদু মন্থর পায়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছেন কবি। কারণ, অন্তরায় এসে কবি চাঁদের কপালে টিপ পরাতে চান, পায়ে রাতের আলো পরাতে চান। তারপর ঝিঁঝির নূপুর শুনতে শুনতে বনের ছায়ায় ঘুমাতে বলেছেন। সঞ্চারীতে কবি ‘সিঁদুর গানরে আকাশ ভরেছি’ বলে গোধূলির বর্ণনা দেন। তারপর আভোগে এসে গোপন কথাটি বলেন মাত্রাবৃত্তের ৬ মাত্রা পূর্ণ পর্ব আর অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রায়—
‘এমন মৌন গোধূলি লগনে
হৃদয়ে হৃদয়ে স্বপনে গোপনে
কিছুবা বলিব কিছু না বলিব
রাতের তিমির ছায়ে’
এই গান সুরে না গাইলেও কেবল পাঠের আবেদনও একটুও কম নয়। ‘ধানখেত’ (১৯৩৩) কাব্যের ‘অবেলায়’ কবিতাটিও আধুনিক মননস্বচ্ছ এক শিল্পসফল গীতিকবিতা।
‘কেন সন্ধ্যায় তুমি এলে
কনক মেঘের অলকায় আজি রঙের কুহেলি মেলে।
গেঁয়ো নদীটির দুটি কূল ধরি
ঝাউ-ঝাড়ে কেশ নাড়ে বিভাবরী
জলের আঙিয়া উড়িয়াছে ভরি
তারি ছায়া বুকে ফেলে।
‘কনক মেঘের অলকা’
‘ঝাউঝাড়ে রাতের চুল নাড়া’ প্রভৃতি অলংকৃত চরণ এ গানটিকে কবিতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কিংবা বলা যেতে পারে, গভীর ব্যঞ্জনাময় কবিতাকেই তিনি গানের আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। ‘একা’ নামের কবিতাটিও গানের নামান্তর।
কারে লয়ে আজ ঘরে ফিরে যাব
এই একা বালুচরে
উদাসী বাতাস ফিরিছে উড়াল
ধুলায় আঁচল ধরে।
আধুনিক গানের আঙ্গিক পুরোপুরি মান্য করেছেন কবি। পল্লিগানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঞ্চারী থাকে না। ঢালাওভাবে তিনি চার-পাঁচ-ছয় অন্তরা একই রকম জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার পল্লিগীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জসীমউদ্দীন আধুনিক গান লিখতে এসে নিজেকে সম্পূর্ণ আধুনিকায়ন করেছেন। আভোগে তাই উচ্চারণ করেন—
তোমার বাহুর সোনার সুতায়
বেঁধে রাখিতাম সাঁঝের ছায়ায়
জল-লহরীর হেরিতাম দোলা
তোমার মামারে ধরে।
অস্থায়ীতে ৬ মাত্রার ২ পর্বের ৩টি চরণ এবং চতুর্থ চরণে ১টি ৬ মাত্রার পর্ব এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। অন্তরায় ৭ মাত্রার দুটি পর্বের দুটি চরণের পরে সেতুবন্ধ চরণ অস্থায়ীর মতো। সঞ্চারীতে ৬+৬/৬+৬/৬+৬/৬+২ মাত্রা এবং আভোগেরা মাত্রা বিন্যাস অন্তরার মতোই। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি নেই। নিখুঁত, নিটোল মাত্রাবিন্যাস। এই কাব্যের শেষ গানটি হলো ‘আমার খেতের ধান’। স্বরবৃত্তে রচিত এ গানটিতেও ছন্দ মাত্রায় নিখুঁত চলন বহমান। ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কাব্যে প্রতিটি সর্গে রয়েছে গ্রাম্য গানের উদ্ধৃতি। হাসু (১৯৩৮) কাব্যে ছোটদের উপযোগী কবিতা স্থান পেয়েছে। রূপবতী (১৯৪৬) কাব্যে দুটি গান রয়েছে ‘অনুরোধ’ আর ‘সন্ধ্যা ডুবে যায়’। দুটিই আধুনিক গান। আধুনিক গান রচনায় কবি মনোনিবেশ করলে পঞ্চ কবির সঙ্গেই উচ্চারিত হতো তাঁর নাম। কিন্তু কবির লক্ষ্য ছিল মাটির গানগুলোকে তুলে আনার দিকে। অনেকেই তাঁকে লোকগীতির সংগ্রাহক হিসেবেই জানেন। আড়ালে থেকে যায় তাঁর গান রচনা, সুর করা এবং কণ্ঠশিল্পীর পরিচয়। কবিতার অঞ্চলে তাঁকে ‘পল্লিকবি’ বলা হলেও আধুনিক বাংলা কাব্যগীতির ধারায় জসীমউদ্দীনের অবস্থানকেই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যায়। আংশিক অবলোকন থেকেই বোঝা যায় যে জসীমউদ্দীন গীতিকবি হিসেবেও জ্যেষ্ঠ এবং অগ্রণী।