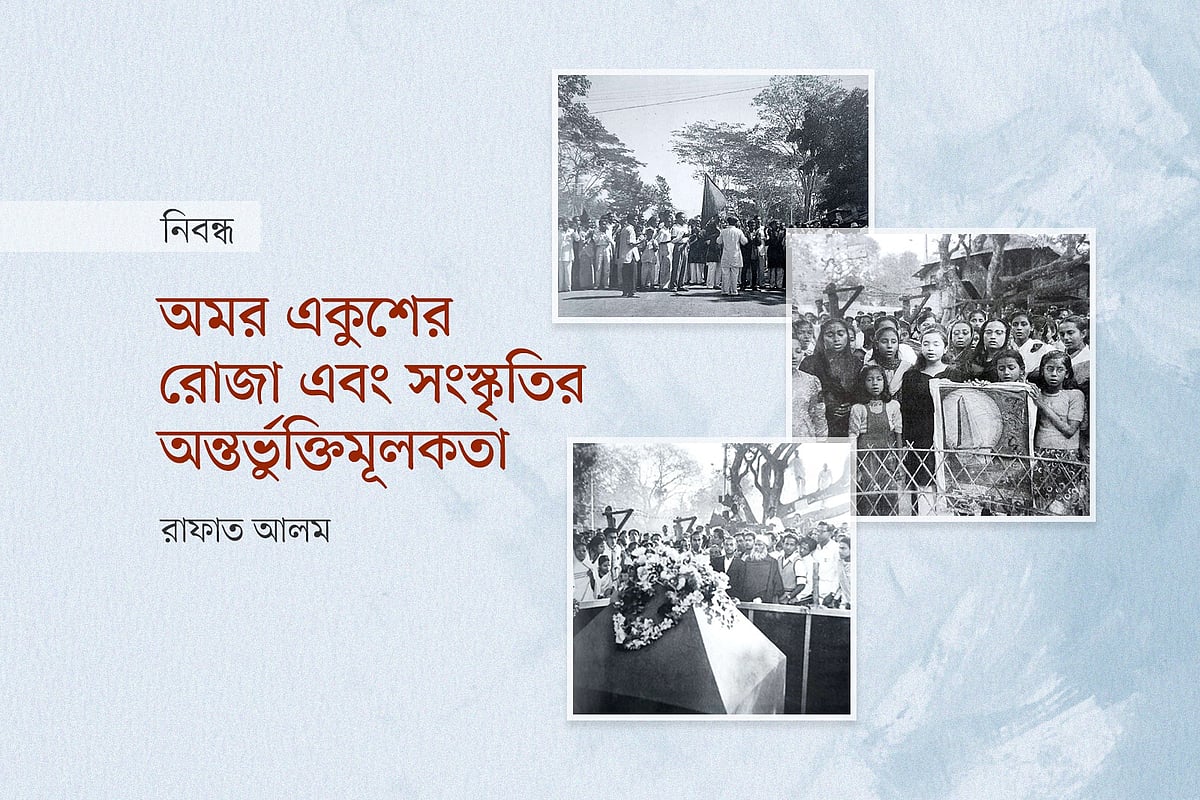১৯৫২ কিংবা তারও পর আরও কয়েক বছরজুড়ে ফেব্রুয়ারিতে পবিত্র রমজান মাস পড়ত না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির রক্তোজ্জ্বল আন্দোলন ও আত্মত্যাগের পর বেশ কয়েক বছর একুশে ফেব্রুয়ারির উদ্যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ রোজা রেখেছিল। এই রোজা রাখা হয়েছিল ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রমাগত অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত স্মৃতিচারণ ’৮০ বইয়ে ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক জানান, ১৯৫৩ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি রোজা রাখার আহ্বান জানায়। ওই বছরের ইত্তেফাক–এর ২৩ ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদন থেকেও জানা যায়, ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের অনেক ছাত্র এদিন রোজা রাখেন। এই ধারা যে বেশ কয়েক বছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে অব্যহত ছিল, তার পরিচয় মেলে ১৯৫৫ সালের একুশের উদ্যাপনের প্রেক্ষাপটে লেখা জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯) উপন্যাসেও। সেখানে দেখা যায়, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহীদদের স্মরণে মুনিম, আসাদ, রাহাত, সালমা, নীলু, বেণুর মতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণেরা রোজা রাখছে; সেই রোজা রমজান মাসে নয়, ফাল্গুন মাসে।
রোজা মুসলমানদের জন্য একটা মৌলিক ধর্মীয় অনুষঙ্গ। রোজা একই সঙ্গে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গও বটে। মুসলমান–অধ্যুষিত বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলাভাষী মুসলমানদের জনসংস্কৃতিতে রোজা-সংস্কৃতিও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু বায়ান্নর একুশে উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে রোজা রাখা যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। বায়ান্নর একুশ আমাদের জনসংস্কৃতির এমন এমন কিছু উপাদানকে উপস্থিত করে, যা সাংস্কৃতিক বাইনারিকে সহজেই ভেঙে দেয়। এই বাইনারি ভাঙতে কোনো বেগ পেতে হয় না। কারণ, আমাদের সংস্কৃতির বহুত্ববাদী চারিত্র্যের মধ্যেই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলকতা। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়পর্বে নানা মত ও পথের মিথস্ক্রিয়ায় ফুলে-ফলে-ফসলে ভরে উঠেছিল অনার্য–অধ্যুষিত শাসককুলের অনাদরণীয় এই বঙ্গীয় বদ্বীপ—আজকের বাংলাদেশ। এই জনাঞ্চলের আভ্যন্তর উদারতার মধ্যে বিকশিত হতে পেরেছিল বিভিন্ন ধর্মীয় মত ও সংস্কৃতি।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির রক্তোজ্জ্বল আন্দোলন ও আত্মত্যাগের পর বেশ কয়েক বছর একুশে ফেব্রুয়ারির উদ্যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ রোজা রেখেছিল। এই রোজা রাখা হয়েছিল ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রমাগত অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে।
একুশের উদ্যাপন আমাদের আরও কিছু জরুরি সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচিত করে। বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে অনেক আন্দোলনকারী নিহত ও নিখোঁজ হলে মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রাতারাতি তৈরি করে শহীদদের শ্রদ্ধার্থে স্মৃতিস্তম্ভ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই তা ভরে ওঠে পুষ্পমাল্যে—শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। পুলিশ তা গুঁড়িয়ে দেয় দুই দিন পরেই। কিন্তু পরের বছর ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকীতে আবারও ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ বিদ্যায়তনে প্রশাসনের নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে এবং সেখানে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। শহীদ মিনার পরিণত হয় প্রতিবাদ ও শোক প্রকাশের স্মারকে। সেখানে ওঠে না কোনো পৌত্তলিকতার প্রশ্ন। বায়ান্ন-পরবর্তী অনেক বছর একুশের উদ্যাপনের নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহীদদের কবর জিয়ারত করা, তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা। একই সঙ্গে ছিল খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা ওড়ানো, একুশের গান গাওয়া এবং শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ। এই ব্যাপারগুলো একসঙ্গেই ঘটেছে। রোজা রাখা, মোনাজাত করা আর শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ সেখানে ঘটেনি।
রোজা একই সঙ্গে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গও বটে। মুসলমান–অধ্যুষিত বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলাভাষী মুসলমানদের জনসংস্কৃতিতে রোজা-সংস্কৃতিও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু বায়ান্নর একুশে উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে রোজা রাখা যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক।
একুশের উদ্যাপনের আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ একুশের গান। প্রথম কয়েক বছর গাজীউল হকের লেখা ‘ভুলব না ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না’ গানটি প্রভাতফেরিতে একুশের গান হিসেবে গাওয়া হতো। এরপর একুশের গান হিসেবে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটি জনপ্রিয়তা পায় এবং এখন তা একুশে ফেব্রুয়ারির অংশ হয়ে গেছে। এই গানে প্রথম সুর দিয়েছিলেন গণসংগীতশিল্পী আবদুল লতিফ। তাতে ছিল অনেকটা রণসংগীতের ধাঁচ। এরপর তাতে নতুন করে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। আলতাফ মাহমুদ গানটিতে খ্রিষ্ট্রীয় প্রার্থনাসংগীত রীতির সুর দেন। খ্রিষ্টীয় প্রার্থনাসংগীত রীতির সংযুক্তি একুশের ফেব্রুয়ারির অন্তর্ভুক্তিমূলকতাকে চিহ্নিত করে। শুধু তা-ই নয়, কালো ব্যাজ পরে প্রভাতফেরিতে খালি পায়ে শোকসংগীত গাইতে গাইতে শহীদ মিনারের দিকে যাওয়ার পুরো আয়োজনের মধ্যে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়ার বিষাদ-শোকের ইমেজটিও অনুভব করা কষ্টসাধ্য নয়। গীতিকার বা সুরকার কেউ যদিও দাবি করেননি, কিন্তু একুশের গানের মধ্যে মর্সিয়া সাহিত্যের অবচেতন প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তখন যেমন ‘মুসলমান’ বা ‘বাঙালি’র বাইনারি ছিল না, তেমনি প্রবল ছিল না এখনকার মতো ‘শিয়া-সুন্নি’র মতবাদগত বৈপরীত্যও।
একুশ উদ্যাপনের একপর্যায়ে যুক্ত হয় শহীদ মিনারকেন্দ্রিক আলপনা। এখানেও অন্তর্ভুক্তিমূলকতার স্পষ্ট ছাপ। সনাতনধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে আলপনার সংস্কৃতি চালু থাকলেও আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতিতে আলপনার ইতিহাস সুপ্রাচীন; এক অর্থে প্রাগৈতিহাসিক। আমাদের চারুশিল্পীরা একুশের উদ্যাপনের সঙ্গে যে আলপনার সংস্কৃতিকে যুক্ত করেন, সেখানেও কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাধান্য কাজ করেনি। আলপনাও হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও শোকের শিল্পিত প্রকাশক। ধর্মীয় বা প্রাণিনির্ভর মোটিফের পরিবর্তে নকশা, স্লোগান ও বায়ান্নর উজ্জ্বল স্মৃতি সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। একুশ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য সংকলন, পত্রিকা এবং পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। সেসবের বিষয়বস্তু বা প্রচ্ছদ-অলংকরণেও মিলবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পচেতনা।
১৯৫৩ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি রোজা রাখার আহ্বান জানায়। ওই বছরের ইত্তেফাক–এর ২৩ ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদন থেকেও জানা যায়, ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের অনেক ছাত্র রোজা রাখেন।
বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি নিঃসন্দেহে এই জনাঞ্চলের মানুষকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখন আমরা ওই চেতনাকে চিনে থাকি ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ হিসেবে। বায়ান্নর পরে, বিশেষত ষাটের দশকে বিকশিত বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্বাধীন বাংলাদেশে, বিশেষত আশির দশক থেকে যেভাবে বাইনারির মধ্যে স্থাপন করা হয়, একুশের সংস্কৃতি মোটেই তার কথা বলে না। মূলত ‘মুসলমানিত্ব’, ‘বাঙালিত্ব’, ‘অসাম্প্রদায়িকতা’, ‘প্রগতিশীলতা’, ‘ধর্মীয় সংস্কৃতি’—এ বিষয়গুলোকে বাইনারি বা বৈপরীত্যের সম্পর্কে স্থাপন করা হয়েছে পরে এবং আরোপিতভাবে। অথচ একুশের উদ্যাপন আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতির দিশা দেখায়। একুশে ফেব্রুয়ারির সামূহিকতা আমাদের এমন এক সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যায়, যেখানে অনেকগুলো সংস্কৃতির উপাদান মিলেমিশে থাকতে পারে। বায়ান্নতে তাৎক্ষণিকতাজনিত যে অপূর্ণতা ছিল, ধীরে ধীরে আরও অনেক অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে একুশ আরও পূর্ণতর হতে থাকে। ‘বাঙালি’ মাত্রই যেখানে কলকাতাকেন্দ্রিক উনিশ শতকীয় ‘বাঙালি’র ধারণা এত দিন প্রভাবশালী ছিল, সেখানে বায়ান্ন-পরবর্তী বাংলাদেশে ‘বাঙালি’র ধারণা অনেক বেশি শক্তিশালী, বহুস্বরিক, প্রায়োগিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। এই বাঙালিত্ব একান্তভাবেই বাংলাদেশীয়, যা মূলত একুশে ফেব্রুয়ারিসঞ্জাত।
একুশের অন্তর্ভুক্তিমূলকতার অন্যতম শক্তির জায়গাটি হচ্ছে এর সেক্যুলার চারিত্র্য। একুশে ফেব্রুয়ারির পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছিল প্রায়োগিক ও ইহলৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আবেগের চেয়ে যথাযথ কার্যকারণ একে বেগবান করেছিল। তাই একুশের সংস্কৃতিতে যে সেক্যুলার বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল, সেখানে ধর্মীয় উপাদান বাদ যায়নি। রোজা-নামাজ-মোনাজাত-মর্সিয়ার মতো ধর্মীয় বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সম্পূর্ণত ইহলৌকিক কর্মসূচির আওতায়। একুশের সংস্কৃতি আরও বেশি লৌকিক ও প্রায়োগিক হতে পেরেছে মুসলমান-অধ্যুষিত জনমানুষের মুসলমানি অনুষঙ্গগুলোকে সহজে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে। একুশের সংস্কৃতি অপরাপর উপাদানকে দূরে সরিয়ে দেয়নি, বাইনারি তৈরি করেনি; সংগ্রামী উপাদানগুলোকে যতটা সম্ভব নিজের করে নিয়েছে। তৈরি হয়েছে একুশের সংস্কৃতির বহুস্বরতা। ধর্মীয় বোধকে বাদ দিয়ে নয়, বরং সঙ্গে করে নিয়েই এই জনাঞ্চলের লোকায়ত ঐতিহ্যে লালিত মানুষ অধিকার আদায়ে, অর্থনৈতিক মুক্তিপ্রশ্নে এবং গণতন্ত্রায়ণে বেশি ক্রিয়াশীল—একুশের অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি আমাদের সেই বার্তা দেয়।