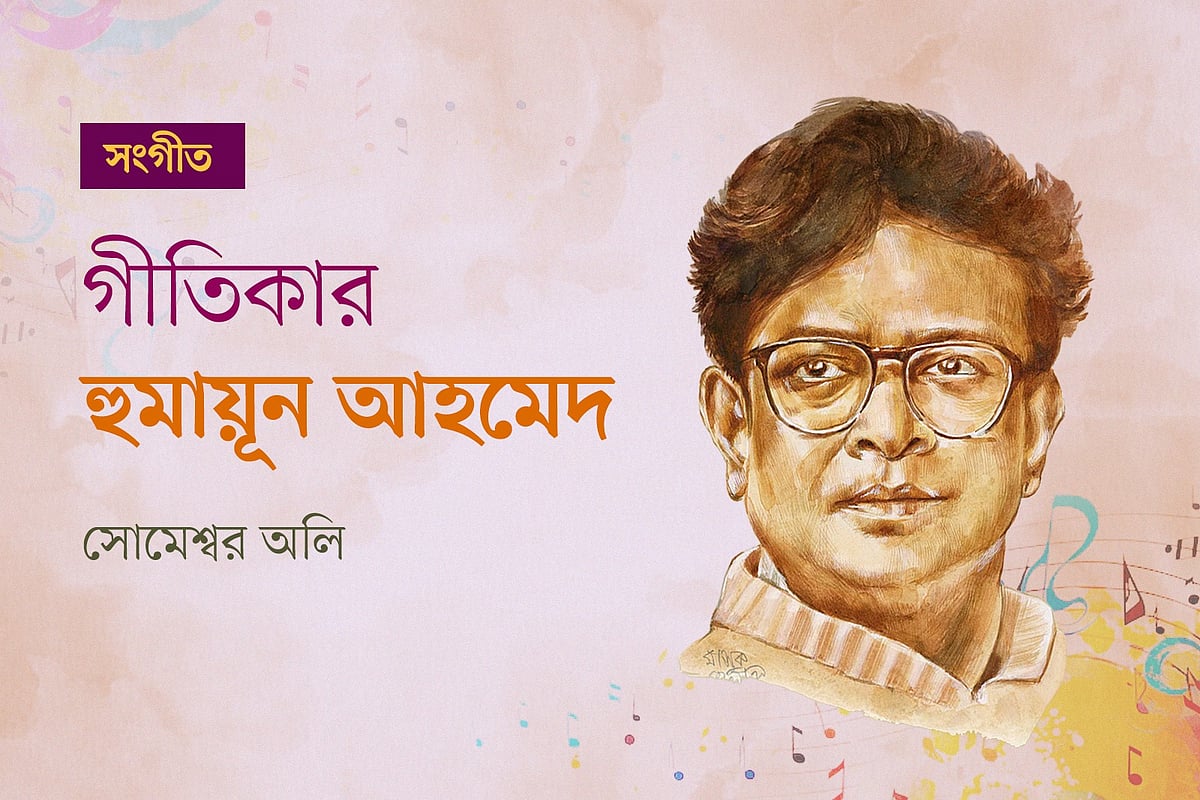কাজল নামের ছেলেটি গান শিখতে চেয়েছিল। পারেনি। ছেলেটির গলায় সুর ছিল না, ছিল না সুরবোধও। গানের ওস্তাদ ভাবলেন, ও তবে তবলা বাজানো শিখুক। কে জানত, কয়েক দিনের মধ্যে ওস্তাদই পালিয়ে যাবেন ছাত্রের দুরবস্থা দেখে! আত্মজীবনীমূলক কোনো একটা বইয়ে এমনটাই উল্লেখ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ, যাঁর আদুরে নাম কাজল। হুমায়ূন অকপটে জানান, তাঁর বাবারও ছিল একই অবস্থা। বাজাবেন বলে শখ করে তিনি বেহালা কিনেছিলেন, শখই রয়ে গেল! এরও আগে, হুমায়ূনের দাদার আমলে তাঁদের পরিবারে গানবাজনা ‘নিষিদ্ধ’ ছিল! অবশ্য এ চিত্র কমবেশি এখনো অনেক পরিবারেই দেখা যায়।
হুমায়ূন আহমেদ নানাভাবেই গানে আশ্রয় খুঁজেছেন। লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাসন রাজা, রাধারমণ, রশীদ উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, উকিল মুন্সী, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ মনীষীর গান শোনার জন্য তিনি আসর বসাতেন। তা সব ব্যবহারও করেছেন নিজের ফিকশনগুলোতে। কিছু প্রচলিত, কিছু অল্প পরিচিত গানেও তিনি নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করেছেন, এনে দিয়েছেন ভিন্ন দ্যোতনা! এই তালিকায় রয়েছে ‘লীলাবালি লীলাবালি’, ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’, ‘সোয়াচান পাখি’ প্রভৃতি। ‘লীলাবালি লীলাবালি’ নিয়ে একটি ঘটনার কথা বলা যাক। বিয়ের গান হিসেবে এ গানটি প্রায়ই গীত হয়। হুমায়ূনের অন্যতম চলচ্চিত্র ‘দুই দুয়ারী’তেও গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ছিল এক ভুল। সেই ভুলের সংশোধনী স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদই দিয়েছিলেন ‘কাঠপেন্সিল’-এর কোনো এক সংস্করণে। সেখানে হুমায়ূন লিখেছেন, ‘লীলাবালি লীলাবালি/ বড় যুবতী সই গো/ কী দিয়া সাজাইমু তোরে” গানের কথায় ভুল আছে। বড় যুবতী হবে না, হবে “বর অযুবাতি”। এর অর্থ, বর আসছে। আমার ভুলের কারণে এখন অন্যরাও ভুল করছেন। শেষে দেখা যাবে ভুলটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আদি ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’
তো ফেরা যাক গীতিকার হুমায়ূন আহমেদের কাছে। ১৯৯০ সালে, ‘অয়োময়’ নাটকে গীতিকার হিসেবে প্রথম পাওয়া যায় তাঁকে। সেখানে তাঁর লেখা একাধিক গীতধর্মী পঙ্ক্তি খালি গলায় পরিবেশন করেছিল চরিত্রগুলো। এরপর ‘কোথাও কেউ নেই’ নাটকে খালি গলায় ‘নাচুনে বুড়ি নাচিল’, আরও কিছু নাটকে কিছু গান লিখেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ সিনেমার চারটি গান দিয়ে গীতিকার হিসেবে সুখ্যাতি আসে তাঁর। যদিও মকসুদ জামিল মিন্টুর সুরে এই সিনেমার ‘একটা ছিল সোনার কন্যা’ গানটি বেশ আগেই রেকর্ড করা হয়েছিল ভিন্ন কারণে। অন্যদিকে বিটিভির ‘রঙের বাড়ই’ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছিল ‘আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা’ গানটি। হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’-এ তাঁর লেখা অন্য দুটি গান হলো ‘ও গো ভাবীজান’ ও ‘কাইল আমরার কুসুম রানীর বিবাহ হইবে’। মজার তথ্য হচ্ছে, ‘আগুনের পরশমণি’ সিনেমার জন্যও গান লিখেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। সত্য সাহার সুরে সেটি গেয়েছিলেন আবিদা সুলতানা। কিন্তু ‘ছবির সঙ্গে যাচ্ছে না’ অজুহাতে গানটি আর প্রকাশ করেননি হুমায়ূন আহমেদ।
বাংলাদেশের গানের সুখ্যাতি শোনা যায়। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, লোকগান, ব্যান্ড কিংবা প্লেব্যাক—সব ক্ষেত্রে একটা স্বর্ণযুগ পেরিয়ে এসেছি আমরা। সেই স্বর্ণযুগের গল্প ঘুরেফিরে কানে আসে। এখন কোন যুগ চলছে, কে জানে! গানের জৌলুশ ফুরিয়ে আসার দিনগুলোতে গীতিকার হিসেবে আবির্ভাব হুমায়ূন আহমেদের। এবার তাঁর লেখার গভীরে চোখ ফেলা যাক।
গীতিকার হুমায়ূন আহমেদের ভাণ্ডারে যেমন বিপুল শ্রোতাপ্রিয় গান আছে, আছে সমাদৃত গানও। গানে শ্রেণিবিভাজনের রেখা মুছে দিয়েছিলেন তিনি, গানের ভাষা ব্যবহারেও সহজতার পক্ষে ছিলেন, ছিলেন আঞ্চলিকতা বা গ্রামীণ শব্দাবলির নান্দনিক উপস্থাপক।
‘নদীর নাম ময়ূরাক্ষী কাক কালো তার জল/ কেউ কোনো দিন সেই নদীটির পায়নি খুঁজে তল/ তুমি যাবে কি সেই ময়ূরাক্ষীতে/ হাতে হাত রেখে জলে নাওয়া/ যে ভালোবাসার রং জ্বলে গেছে/ সেই রংটুকু খুঁজে পাওয়া...’
একান্ত ব্যক্তিগত কারণে এটি লিখেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। এস আই টুটুল এর সুর করেছিলেন। পরে অবশ্য গানটি ‘আমার আছে জল’ চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়। হুমায়ূন আহমেদ পেশাদার গীতিকার ছিলেন না। তাই আইটেম নাম্বার বা ‘পাবলিক খায়’ এমন লেখার ফরমায়েশ আসেনি তাঁর কাছে। সুরকারের নির্দেশনা, মাতব্বরি বা প্রযোজকের চাহিদাও পূরণ করতে হয়নি লেখার এই বাদশাহকে। বরং তিনি প্রচলিত ফরম্যাট না মেনে, যা লিখেছেন তাতেই সুরারোপ করা হয়েছে। যেমন ইচ্ছা শব্দ-ভাবনা নিয়ে খেলেছেন গানের খাতায়। প্রিয়জনের মান ভাঙাতে হোক, খেয়ালের বশে কিংবা নিজের নাটক-চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই হোক, কিছু অবিস্মরণীয় গান লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তিনি হয়তো জানতেন গানগুলোর অধিকাংশই হয়ে উঠবে শ্রোতাপ্রিয়, অবিনশ্বর হয়ে থাকবে সমকালীন গানের পটভূমিতে আর সেগুলো একে একে নাম লেখাবে মহাকালের ইতিহাসে!
গীতিকার হুমায়ূন আহমেদের ভাণ্ডারে যেমন বিপুল শ্রোতাপ্রিয় গান আছে, আছে সমাদৃত গানও। গানে শ্রেণিবিভাজনের রেখা মুছে দিয়েছিলেন তিনি, গানের ভাষা ব্যবহারেও সহজতার পক্ষে ছিলেন, ছিলেন আঞ্চলিকতা বা গ্রামীণ শব্দাবলির নান্দনিক উপস্থাপক। অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা গানে ব্যবহার-অযোগ্য অনেক শব্দকে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। উপরে উল্লিখিত গানটির লিরিকে ‘কাক কালো তার জল’-এর ব্যবহার সেটিই মনে করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে তাঁকে দেখি, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ করছেন অহরহ, মুরব্বিদের বিচারে দূষণীয় হলেও একই গানে রাখছেন ‘তার’, ‘তাহার’—দুটোই। হুটহাট দেখা যায় এমন পঙ্ক্তি—‘যখনই আকাশ কালো হয়/ মেঘবতীদের উড়িবার তখনই সময়…’ (যে থাকে আঁখি পল্লবে)। এখানে লক্ষণীয় শব্দটি হচ্ছে, ‘উড়িবার’।
হুমায়ূন আহমেদ কিছু বিষয়ের প্রতি আজীবন দুর্বলতা দেখিয়েছেন, পক্ষপাতিত্ব করেছেন, এমনকি এসব নিয়ে বাড়াবাড়িও করেছেন। এর মধ্যে চাঁদ, জোছনা, বৃষ্টি, সাগর, জল, নদী, পাখি প্রভৃতি অনুষঙ্গ অন্যতম। গল্প-উপন্যাসের বাইরে তাঁর লিরিকে এসব উপাদান এসেছে ঘুরেফিরে। তাঁর লেখা অধিকাংশ গানই জোছনা, চাঁদ, বৃষ্টি কিংবা জলে ঠাসা। চাঁদ শুধু চাঁদ নয়, বৃষ্টিও বৃষ্টি নয়, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঞ্জনার স্মারক হিসেবে হাজির হয়েছে। আর এসব তিনি ঘিরে রেখেছেন বিষণ্ণতার প্রলেপ আর সুরের কারসাজি দিয়ে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হুমায়ূনের ছিল একটা কবিমন, যে কিনা কবি হতে পারেনি বা চায়নি, গানে গানে সে কথাগুলোই অকপটে তিনি বলেছেন, নিজের কবিসত্তার প্রতি পূর্ণ ইমান রেখে।
‘যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়’—কথাগুলো রোমান্টিক ভাবনায় রচিত হলেও গানটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে বিষণ্নতা, হাহাকার ও মিশ্র অনুভূতি। এ গান শুনে বিষাদগ্রস্ততা পেয়ে বসে যেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ধীর লয়ের মতো এই গানের কবিতাখানি। বৃষ্টির দিনে বা বৃষ্টিহীন অবসাদে এই গান কতজনকে যে আক্রান্ত করে, সেই হিসাব কি দিতে পারবে স্পটিফাই!
হুমায়ূন মৃত্যুচিন্তাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন জোছনা বা চান্নি-পসর দিয়ে। এবং অমোঘ নিয়তির মৃত্যু যেন সুন্দর মুহূর্তে হয়, তারই প্রার্থনাসংগীত রচনা করেছেন এ মানুষটি, ভাবা যায়! ‘ও কারিগর দয়ার সাগর ওগো দয়াময়/ চান্নি-পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়’। এস আই টুটুলের কণ্ঠে আধ্যাত্ম ভাবনার এই গান শুনে চিন্তিত ও বিচলিত বোধ হতে থাকে। এখানে ‘চান্নি-পসর’ শব্দ দুটির ব্যবহার ‘হুমায়ূনীয় কায়দা’রই অকাট্য দলিল। জীবনের বিষণ্নতা বা বিপন্নতাকে মেলে ধরার জন্য তিনি জোছনাকে গ্রহণ করেছেন, যে জোছনা বড় গগনবিদারী ও অনন্ত শূন্যতার এক চরাচর বলে ভ্রম হয়। সেলিম চৌধুরীর গাওয়া ‘চাঁদনি-পসরে কে আমারে স্মরণ করে/ কে আইসা দাঁড়াইছে গো আমার দুয়ারে’ কিংবা শাওনের কণ্ঠে ‘আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা ভাঙা বেড়ার ফাঁকে/ অবাক জোছনা ঢুইক্যা পরে হাত বাড়াইয়া ডাকে’ গানগুলো শুনে অপার্থিব এক দুনিয়া দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।
লক্ষ করার মতো বিষয়, জোছনার মতো পানি বা জলও হুমায়ূনের আরেক প্রিয় আশ্রয়। সেই জল হতে পারে বৃষ্টির, হতে পারে চোখের কিংবা পদ্মপুকুরের। ঘুরেফিরেই জলের কাছে দুঃখ লুকাতে চাইতেন কি তিনি? দেখতেন কি জলের আয়নায় নিজেকেই? এ কারণে হুমায়ূনের সৃষ্টি করা চরিত্রেরা কখনো কখনো কারণে-অকারণে ভিজতে থাকে বাদল কিংবা চোখের জলের বৃষ্টিতে, আর ভেজায় পাঠক-দর্শকের মনকেও।
শাওনের কণ্ঠে ‘যে থাকে আঁখি পল্লবে/ তার সাথে কেন দেখা হবে/ নয়নের জলে যার বাস/ সে তো রবে নয়নে নয়নে’ কিংবা হাবিব ওয়াহিদের সুরে (সাবিনা ইয়াসমীন, শাওন, হাবিব গেয়েছেন একাধিক সংস্করণে) ‘যদি ডেকে বলি এসো হাত ধরো/ চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে/ এসো গান করি মেঘমল্লারে/ করুণাধারার দৃষ্টিতে’ গান দুটি একই সঙ্গে রোমান্টিকতার কথা বলে আবার বিরহও জাগিয়ে দেয়। এই দ্বিচারিতার দেখা মেলে হুমায়ূনের আরও আরও গীতিকবিতায়, রচনায়।
অবশ্য এ বৈশিষ্ট্যের কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে ‘আমার আছে জল’ গানটিতে। একাকী উচ্ছল কিশোরীর মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে হুমায়ূন গানটির শুরুর অংশে লিখেছেন, ‘...সেই জল যেন পদ্মপুকুর/ মেঘলা আকাশে মধ্য দুপুর/ অচেনা এক বনবাসী সুর বিষাদে কোমল’। বিষাদও কখনো কখনো কোমল হয়, জানালেন হুমায়ূন।
প্রকৃতির কাছে কতখানি সমর্পিত হলে, জলের প্রতি কতটা আকর্ষণ বোধ করলে কেউ বলতে পারে ‘আমি আজ ভেজাব চোখ সমুদ্র-জলে/ ও সমুদ্র কাছে আসো/ আমাকে ভালোবাসো/ আদরে লুকায়ে রাখো তোমার ওই অঞ্চলে’? আবার একই লিরিকে তিনি জোছনা ও বরষার সম্মিলন ঘটিয়েছেন এমন গানও আছে। ‘বরষার প্রথম দিনে’ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
জোছনা-বৃষ্টি-জল-বিষণ্নতা-বিপন্নতা দিয়ে হুমায়ূন তাঁর গানের এমন একটি জগৎ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেটি তাঁরই নিজস্ব, তাঁর স্টাইল কিংবা একগুয়েমির সারাৎসার। এর সঙ্গে আর কাউকে মেলানো যায় না, তা অসম্ভব।
জোছনা-বৃষ্টি-জল-বিষণ্নতা-বিপন্নতা দিয়ে হুমায়ূন তাঁর গানের এমন একটি জগৎ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেটি তাঁরই নিজস্ব, তাঁর স্টাইল কিংবা একগুয়েমির সারাৎসার। এর সঙ্গে আর কাউকে মেলানো যায় না, তা অসম্ভব। এর বাইরে, হুমায়ূনের গানে আরও কিছু ব্যাপার লক্ষণীয়। এর মধ্যে আছে তাঁর সরস মনের পরিচয়, গল্প বলার প্রবণতা, অদ্ভুত ও গ্রামীণ শব্দ প্রয়োগ, অন্ত্যমিলে মুনশিয়ানা আর চমকের ব্যবহার। তবে সবই সহজাতভাবে রচনা করেছেন তিনি। আর এসবের ভিজ্যুয়ালাইজেশনও হয়েছে লেখকের মনের মতো করে। এমন স্বাধীনতা নিয়ে, বঙ্গে, জন্মায় কোন সে গীতিকার?
ভাবনায় ফেলে দেওয়ার মতো একটি লিরিক হলো, ‘মাথায় পরেছি সাদা ক্যাপ/ হাতে আছে অচেনা এক শহরের ম্যাপ/ ব্যাগ ঝুলিয়েছি কাঁধে/ নামব রাজপথে/ চারিদিকে ঝলমলে রোদ/ কেটে যাবে আঁধারেরই ছায়া অবরোধ/ চারিদিকে কী আনন্দ/ অতি তুচ্ছ পতঙ্গের অপূর্ব জীবন/ হয়তো শিশিরকণারও আছে শুধু তার একান্ত একা আনন্দেরই ক্ষণ’। ‘অতি তুচ্ছ পতঙ্গের অপূর্ব জীবন’—এই চিত্রকল্প আবিষ্কার যেনতেন গীতিকারের কাজ তো নয়! এর জন্য চাই হুমায়ূনীয় শক্তি।
গল্প বলা গানগুলোর মধ্যে সুপারহিট মকসুদ জামিল মিন্টুর সুরে সুবীর নন্দীর গাওয়া ‘একটা ছিল সোনার কন্যা’। হুমায়ূনের ৯০ শতাংশ কাজের (সুর, সংগীতায়োজন ও আবহসংগীত) একচ্ছত্র অধিকারী মিন্টু। এই গানের ‘সবুজবরণ লাউ ডগায় দুধসাদা ফুল’ চিত্রটি অন্য রকমভাবে ধরা দেয়। এ গানটির বড় শক্তি—সহজ কথা, সহজ সুর। এতটাই সহজ যে আগে থেকেই দৃশ্যকল্পগুলো আমাদের চোখের সামনে বিরাজমান, হুমায়ূন কেবল পরিবেশন করেছেন অকঠিন ভঙ্গিমায়। অন্যদিকে তাঁর সরস মনের পরিচয় পাওয়া যায় ‘তোমার ঘরের সামনে ছোট্ট ঘর বানাব গো’-সহ আরও কিছু গানে।
কথিত আছে, হুমায়ূন আহমেদের ‘দখিন হাওয়া’য় গানের আসরে সূচনা সংগীতে থাকতেন হাসন রাজা, শেষ হতো ‘মরণসংগীত’ দিয়ে। বাউল গিয়াস উদ্দিনের লেখা ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ হলো সেই মরণসংগীত। আর আসরের মাঝখানে থাকত রবীন্দ্রনাথের গান। হুমায়ূন বিভিন্ন মনীষীর গান শুনে চোখের জল ফেলতেন, এসবই কিংবদন্তি হয়ে আছে সতীর্থদের মনে, স্মৃতিতে। হুমায়ূনের সবচেয়ে প্রিয় গান কোনটি জানেন? নিজের গান তো অবশ্যই নয়, সেটির গীতিকার স্বয়ং রবিবাবু। গানটি হলো, ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না...’