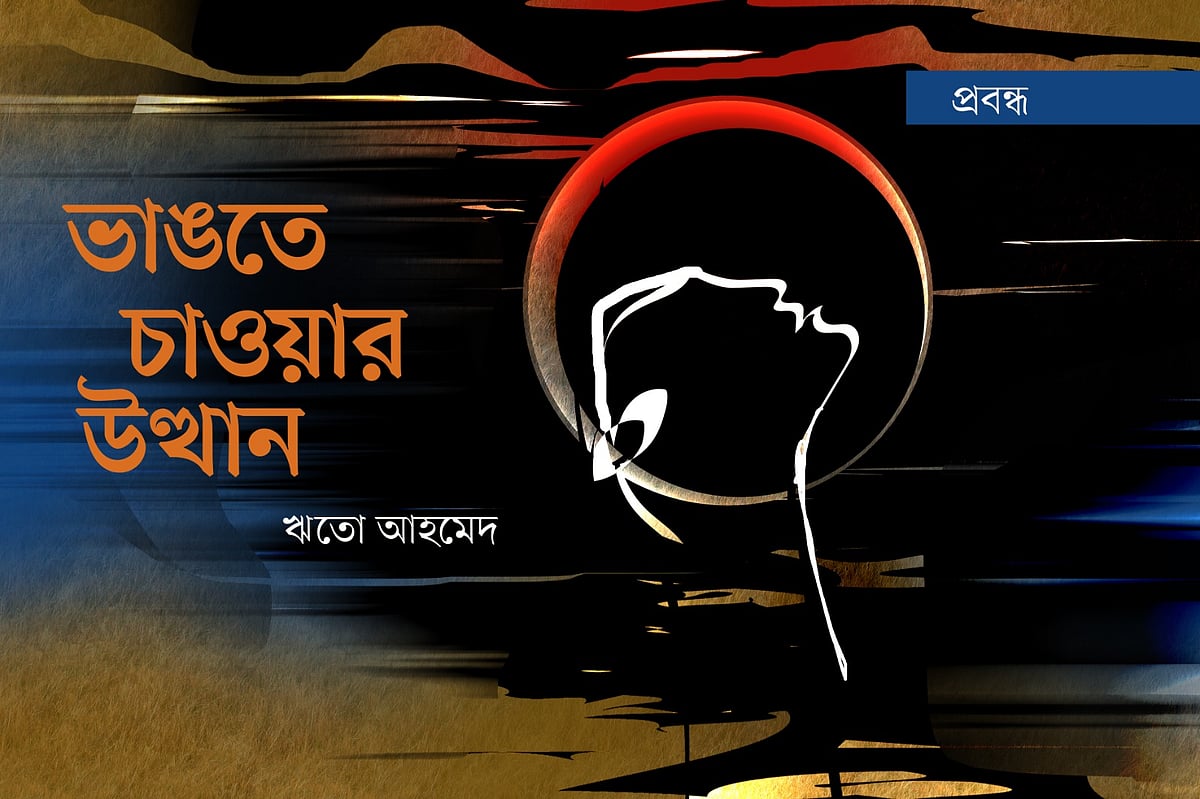এই কিছুদিন আগেই তো বহু মানুষের ভেতর থেকে বেলারুশের কবি ও গায়ক ভ্লাদিমির লেনকেভিচকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি ‘কুপালিঙ্কা’ গাচ্ছিলেন রাস্তায়। ‘কুপালিঙ্কা’ হচ্ছে একটা গান যেটা লিখেছিলেন আরেক বেলারুশীয় কবি মিশেজ জার্যনট, যাঁকে ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি শেষ কবিতাটি লিখে রেখে গিয়েছিলেন জেলখানার দেয়ালে, যখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, ‘দেশে দেশে কালে কালে বাক্রোধ করার চেষ্টায় এই নৃশংসতা কীভাবে চলে, আর কীভাবেই বা তার থেকে উত্তরণেরও একটা স্বপ্ন–আশ্বাস থেকে যায় দর্পিত মানুষের মনে’! বলেছিলেন ‘অজেয় লিপি’ নামের ব্রেখটের সেই কবিতার কথা, যেখানে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালীয় এক জেলবন্দীর কথা। জেলের দেয়ালে কপিং পেনসিল দিয়ে সেই বন্দী, সোশ্যালিস্ট সৈনিক লিখেছিলেন: ‘দীর্ঘজীবী হোন লেনিন’। জেলারের নির্দেশে একবালতি চুন দিয়ে মুছে দেওয়া হলো সেই লেখা। মুছে তো গেলই না, বরং অক্ষরগুলোর ওপর চুন বুলিয়েছিল বলে আরও জ্বলজ্বল করে উঠল লেখাটা। গোটা দেয়ালে তখন বুলিয়ে দেওয়া হলো চুন। চুন শুকিয়ে যেতেই আবারও ফুটে উঠল সেই লেখা। তখন একটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নেওয়া হলো অক্ষরগুলো। ফলে দেয়ালে এবার গভীর করে খুঁড়ে তোলা অক্ষরগুলো পড়া গেল। তখন সৈনিকটি বলে উঠল, ‘এবার তবে দেয়ালটাকেই ভাঙো।’ আবার আমাদের মনে পড়ে যে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় গুলি করে মারা হয়েছিল লোরকাকে (১৯৩৬)। সমবেত জনতার সামনে দিয়েই হাতে শিকল বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কবিকে। অস্ফুট হৃষ্টতায় কবি তখন উচ্চারণ করছিলেন, ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, মানুষের মুক্তি আসুক। আমার শিকল খুলে দাও।’ কিন্তু তাঁকে গুলি করা হলো। প্রথম গুলি কানের পাশ দিয়ে গেল। কবি হাসলেন। দ্বিতীয় গুলিতে তাঁর বুক ফুটো হয়ে গেল। তৃতীয় গুলি ভেদ করে গেল তাঁর কণ্ঠ। কিন্তু তবু কবি শান্তভাবে বললেন, ‘আমি মরব না।’ চতুর্থ গুলিতে বিদীর্ণ হলো কপাল। যে খুঁটিতে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল, পঞ্চম গুলিতে মড়মড় করে উঠল সেটা। আর ষষ্ঠ গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল তাঁর ডান হাত। মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে কবি বলতে চাইলেন, ‘বলেছিলাম না, আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না।’
আমি বুঝতে পারছি খুন করা হয়েছে আমাকে।
তারা কাফে, কবরখানা আর গির্জাগুলো
তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।
তারা সমস্ত পিপে আর কাবার্ডগুলো
তছনছ করছে।
তিনটে কঙ্কালকে লুট করে
খুলে নিয়ে গেছে সোনার দাঁত।
আমাকে তারা খুঁজে পায়নি।
কখনোই কি পায়নি তারা?
[অমিতাভ দাশগুপ্ত ও কবিতা সিংহের ‘লোরকার শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বই থেকে]
সৈনিক লিখেছিলেন: ‘দীর্ঘজীবী হোন লেনিন’। জেলারের নির্দেশে একবালতি চুন দিয়ে মুছে দেওয়া হলো সেই লেখা। অক্ষরগুলোর ওপর চুন বুলিয়েছিল বলে আরও জ্বলজ্বল করে উঠল লেখাটা। গোটা দেয়ালে তখন বুলিয়ে দেওয়া হলো চুন। চুন শুকিয়ে যেতেই আবারও ফুটে উঠল সেই লেখা। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নেওয়া হলো অক্ষরগুলো। দেয়ালে এবার গভীর করে খুঁড়ে তোলা অক্ষরগুলো পড়া গেল। তখন সৈনিকটি বলে উঠল, ‘এবার তবে দেয়ালটাকেই ভাঙো।’
নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক
‘ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের সময়, অনেক বিপ্লবী সাহিত্য ব্রিটিশরা নিষিদ্ধ করেছিল। কারণ, এগুলো তৎকালীন ভারতে তাদের শাসনের “নিরাপত্তা”র পক্ষে “বিপজ্জনক” হয়ে উঠেছিল।’—ইন্ডিয়ানএক্সপ্রেসডটকমের এ রকমই একটা সংবাদে এসে চোখ পড়ে সেদিন। দিনটি ছিল ৯ই জুলাই ২০২২। ‘স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে সরকার এখন সাহিত্যের এই অংশ আবার তুলে ধরছে। পরাধীন ভারতের সেই লেখাগুলোকে জনপ্রিয় করার জন্য অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকেও কাজে লাগানো হয়েছে।’—বেশ ভালো লাগছিল পড়ে। ‘স্বাধীন স্বর’ নামে অমৃত মহোৎসব ওয়েবসাইটের একটি অংশে বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি, কন্নড়, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু ও উর্দু ভাষায় ১৯৪৭ সালের আগে লেখা কবিতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক, ৭৫ সপ্তাহব্যাপী এই অমৃত মহোৎসবে ব্রিটিশ রাজের নিষিদ্ধ করা কবিতা, লেখা ও প্রকাশনাগুলো চিহ্নিত করেছে। সেই সব লেখাকে ক্যাটালগ আকারে একত্র করেছে, যা ন্যাশনাল আর্কাইভসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ৯টি আঞ্চলিক ভাষা—বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, তেলেগু, তামিল ও উর্দু ভাষায় সেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো বেশির ভাগই ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় লেখা। এই সুন্দর কাজও রাষ্ট্রই করছে। আবার আমাদের মনে পড়ছে কবি একরাম আলির ওই কথাও, ‘কবিতা প্রকৃতপক্ষে এমনই, যা হৃদয় পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়ার চেয়েও ভয়ংকর। কবিতার যে সর্বগ্রাসী ধ্বংসোন্মুখতা আছে, অন্তত কবির জীবনে, হাঙরের ঢেউয়ে সাঁতার কাটার বিপজ্জনক সেই তরঙ্গকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম।...দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রই প্রকৃত কবি ও তাঁর কবিতাকে স্বাগত জানাতে পারেনি। রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির সৃষ্টিকর্মকে সহ্য করতে পারে না যে!’
শুধু ব্রিটিশ আমলেই নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের নিরাপত্তায় বিপজ্জনক হয়ে উঠলে গুম/খুন হয়ে যাওয়ার মতো বহু উদাহরণও দেখেছি আমরা এই সময়ে এসেও। আমাদের মনে আছে, বাংলাদেশের লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর কথা। জেলের ভেতর পুলিশি নির্যাতনে যাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২০২১ সালে। তাঁর অপরাধ ছিল কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের বিতর্কিত কার্যকলাপের সমালোচনা করা। দেখেছি বরিশালের কবি হেনরি স্বপনের জেলে যাওয়া। আর ঢাকার রাজপথের দেয়ালে দেয়ালে যেসব গ্রাফিতি এঁকেছিলেন হবেকি’র শিল্পীরা (সুবোধ তুই পালিয়ে যা, এখন সময় পক্ষে না), সেগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করে, ভয় দেখিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। কিন্তু সত্যিই কি মুছে দেওয়া যায় আসলে? নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া গেছিল ‘অগ্নিবীণা’র ‘বিদ্রোহী’কেও?
বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি’ আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি’
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব–বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির–উন্নত শির!’
গ্রেপ্তারের পর তাঁকে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৬ জানুয়ারি বিচারের পর নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে। এখানে যখন বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন, তখন (১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যগ্রন্থটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। এতে নজরুল বিশেষ উল্লসিত হন। এই আনন্দে জেলে বসেই ‘আজ সৃষ্টি–সুখের উল্লাসে’ কবিতাটি লিখে ফেলেন।
হ্যাঁ, এই কবিতা সেই সময় নিষিদ্ধ করা হবে কি না, সেটা নিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের মধ্যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলেও যেখানেই এসব পত্রিকা পেত, সেগুলো জব্দ করত। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল নজরুলের অন্য পাঁচটি বই। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ প্রকাশিত হয়। এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় ৮ নভেম্বর পত্রিকার উক্ত সংখ্যা নিষিদ্ধঘোষিত হয়। একই বছরের ২৩ নভেম্বর তাঁর ‘যুগবাণী’ প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং একই দিনে তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি নজরুল ‘বিচারাধীন বন্দী’ হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবানবন্দি প্রদান করেন। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে তিনি এই জবানবন্দি দিয়েছিলেন। তাঁর এই জবানবন্দি বাংলা সাহিত্যে ‘রাজবন্দীর জবানবন্দি’ নামে বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই জবানবন্দিতে নজরুল বলেন:
‘আমার ওপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।...আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন, আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যাদ্রোহী নয়। সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচার দগ্ধ করবে...।’
১৬ জানুয়ারি বিচারের পর নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে। এখানে যখন বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন, তখন (১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যগ্রন্থটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। এতে নজরুল বিশেষ উল্লসিত হন। এই আনন্দে জেলে বসেই ‘আজ সৃষ্টি–সুখের উল্লাসে’ কবিতাটি লিখে ফেলেন।
ভাঙতে চাওয়ার উত্থান
আবার এমনই এক সৃষ্টির উল্লাসে অন্য রকম কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন গত শতাব্দীর সেই ৬০–এর দশকের কয়েকজন তরুণ। নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কবিতার জগৎ, সাহিত্যের পৃথিবী। যেসব কবিতা লেখার অপরাধে আদালতে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল তাঁদের। জেল খাটতে হয়েছিল। জরিমানা গুনতে হয়েছিল। কাউকে কাউকে মুচলেকা দিয়েও ছাড়া পেতে হয়েছিল। চাকরি খোয়াতে হয়েছিল। হ্যাঁ, তাঁরা ছিলেন হাংরি জেনারেশনের কবি। কী এক প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতারে কেঁপে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের মহল! জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা, শিল্প নামে কোনো অলীক কাণ্ড কোথাও নেই, কবিতা কোনো দৈব সূত্রে পাওয়া সাজানো-গোছানো বিলাসব্যাপার নয়। জীবনযাপনেরই সত্য প্রকাশ হলো কবিতা। সেদিন তাঁদের প্রকাশের ওই ধরনকে তখনকার নীতিবাহকেরা খুব একটা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি। তাই হয়তো শ্রদ্ধেয় আবু সায়ীদ আইয়ুবের অনুরোধে তৎপর হয়ে ওঠে কলকাতা পুলিশ। কী বলেছিলেন তাঁরা? কবিতাকে কীভাবে দেখতে চেয়েছিলেন? তাঁদের বুলেটিনে বলেছিলেন, ‘কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়। অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়। নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতায় সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজনে এমনভাবে আবির্ভূত যে জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী-বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ ক্ষুধার কেবলমাত্র লালনকর্তা কবিতা। কারণ, কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে। মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।’
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লেখেন, ‘আপনাদের বক্তব্য আমি স্বীকার করি না। কিন্তু বুঝতে পারি যে অনির্বাচিত মানবস্বভাব আপনাদের উপপাদ্য। প্রসঙ্গত জানাই, আপনার সমীক্ষাধর্মী প্রবন্ধ বা কবিতাসম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর ভাবনার একটা তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হয়েছে।...কবিতায় আপনাদের প্রতিবাদমুখর নন্দনসংবিতের বলিষ্ঠতা এবং দার্শনিক ভঙ্গিটির ছাপ আমি খুঁজে পাইনি। আপনাদের নন্দনতত্ত্ব বোধয় প্রায় তৈরি, কিন্তু কবিতা এত দুর্বল, এত অসহায় কেন?’ অমিতাভ দাশগুপ্ত বলেন, ‘ভালো লাগার মতো একটা নোংরা আবদেরে কথা আমি বলব না—বহু ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, কিস্যু ঠিকমতো হচ্ছে না, কোথাও বিটকেলপনা হচ্ছে, তবু মনে মনে রীতিমতো আক্রান্ত ও অসহায় বোধ করছি।’
প্রতিষ্ঠানকে কিংবা নীতিবাহকদের কীভাবে আক্রান্ত করেছিলেন সেই কবিরা? আঘাতটা কোনখানে পৌঁছাচ্ছিল তখন, যার পরিপ্রেক্ষিতে অমন ক্ষমাহীন প্রত্যাঘাতের আয়োজন হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে? অবশ্য তাঁদের ওই আবির্ভাব বাংলা কবিতায় নতুন দিকবদলের ইঙ্গিত বহন করেছিল অনেকের কাছেই। অনেকেই ভাবছিলেন, তাঁদের এই বহিঃপ্রকাশের ধরনই মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের সামাজিক পচন কোন সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিসের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ? ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বুঝে নিতে চেয়েছেন হাংরি বিদ্রোহের লক্ষণগুলোও। আমরা জেনেছি যে প্রতিষ্ঠানকে ভাঙতে চাওয়া যৌবনের ধর্ম। জীবনকে মৃত্যুর সামনে রেখে দেখা, মৃত্যুকে জীবনের সামনে রেখে দেখা যৌবনের ধর্ম। তাই তো কবিকে বলে যেতে হয় তাঁর একেবারে নিজস্ব কথা, ব্যক্তিগত উদ্ঘাটন, তাঁর হীনতা–তুচ্ছতা–পরাভবসুদ্ধ তাঁর উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকার কষ্ট আর উল্লাস। কিন্তু সবার কথা বলা আর সবার জন্য বলা এক কথা নয়। নিজের সব ভন্ডামির চেহারা মেলে ধরা, সভ্যতার নোনা পলেস্তরা মুখ থেকে তুলে ফেলা কিংবা যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে, তাকে সন্দেহ করাব—এভাবেই তো এগিয়েছিলেন তাঁরা।
হাংরি সাহিত্য আন্দোলন ১৯৬১ সালে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে শেষ হয়ে যায়। সাড়াজাগানো এই আন্দোলন বদলে দিয়েছে আজকের কবিতা লেখার অভিমুখ। বদলে দিয়েছে কবিতার ভাষা। কবিতা রচনায় এমন সব শব্দ সম্বন্ধ তৈরি করেছিলেন তাঁরা, যা ওই সময়কালে উচ্চারণ করার স্পর্ধা একমাত্র তাঁরাই দেখাতে পেরেছিলেন। ফলে কবি মলয় রায়চৌধুরীসহ পাঁচজন কবির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ নামক কবিতাটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে।
‘আমিই সেই আরতি—তুমিও কি আমাকে চেনো না?
যখন আমরা নেংটো, তখনই জানতে চাই তার নাম
যখন আমরা নেংটো, জিজ্ঞেস করি এটা কোন গ্রাম
শ্মশানের শেষ আর বসতির শুরু, এই যে নদীর বাঁক
এখানেই কে তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে লুকানো এই গুহা
কে তোমাকে খুলে দিয়েছে এই জীবন, মৃতের ওপর নেচে ওঠা?’
[কুমারীর গুহা/অরুণেষ ঘোষ]
হাংরি সাহিত্য আন্দোলন ১৯৬১ সালে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে শেষ হয়ে যায়। সাড়াজাগানো এই আন্দোলন বদলে দিয়েছে আজকের কবিতা লেখার অভিমুখ। বদলে দিয়েছে কবিতার ভাষা। কবিতা রচনায় এমন সব শব্দ সম্বন্ধ তৈরি করেছিলেন তাঁরা, যা ওই সময়কালে উচ্চারণ করার স্পর্ধা একমাত্র তাঁরাই দেখাতে পেরেছিলেন। ফলে কবি মলয় রায়চৌধুরীসহ পাঁচজন কবির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ নামক কবিতাটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। নিম্ন আদালতে মলয় রায়চৌধুরীর সাজা হয়ে যায়। আমরা দেখতে পাই, তাঁদের ইশতেহারে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, ‘কবিতা চলাকালীন আমার সম্মুখে আমাকে এবং আমার সমস্ত কিছুকে যত রকমভাবে পারা যায় উপস্থিত করা। কবিতায় আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আটক করে ফাঁস করা যখন আমি কোনো না কোনো কারণে ফেটে পড়েছি আর আমার ভেতর দিকটা বেরিয়ে পড়েছে। নিজস্ব অহং দিয়ে প্রতিটি মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ, তারপর স্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যান। কবিতায় আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত সমস্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান, আর বাইরের কোনো রকম ঘুষ না দিয়ে কবিতাকে নিজেই মৌলিক হতে দেওয়া। কবিতাই মানুষের সর্বশেষ ধর্ম। আর ঈশ্বর জঞ্জাল।’
হ্যাঁ, জীবনকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষতায়ই মেলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁরা কবিতায়।
জন্মই আমার আজন্ম পাপ
আবার কবিতা লেখার অপরাধে চারটি দশক ধরে এক কবিকে আটকে রাখা হয়েছে স্মৃতির কারাগারে। যে দেশে অজস্র যুদ্ধাপরাধী দম্ভের পতাকা উড়িয়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, সেখানে কবিতা লেখার অপরাধে একজন কবি প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরতে পারেন না—বড়জোর প্লেনের জানালা দিয়ে একনজর দেখতে পারেন ফালি ফালি শস্যখেত, মনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে হয়তো ‘ওইখানে পাবনা, ওইখানে ইছামতী’! দেশের যদি হাত থাকত, দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিত। কিন্তু দেশ তো শাসনের ম্যান্ডেট, ক্ষমতার আস্ফালন, কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলতার দোর্দণ্ড প্রতাপ, দেশ তো ব্লাসফেমি কবিতা লেখার অপরাধে মাথা কেটে নেবার ফতোয়া।
দাউদ হায়দারকে ভারত থেকেও বহিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভারত সরকার তাঁকে ভারত ত্যাগের ফাইনাল নোটিশ দিয়ে দেয়।’ এমন এক দুঃখকালে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান কবিবন্ধু নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত কবিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ’৮৫-এর কোনো এক ভোরে জার্মানির বার্লিনে গিয়ে পৌঁছান দাউদ হায়দার।
বাংলাদেশের এই একজন কবিই আছেন যিনি কবিতা লেখার অপরাধে নির্বাসিত। জার্মানিতে কী নেই? সব আছে। কিন্তু কোথাও দাউদ হায়দারের ‘ইছামতী নদী’ নেই! একটি কবিতা লেখার অপরাধে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন অগ্রসর ভাবনার কবি দাউদ হায়দার। দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন সত্তর দশকের শুরুর দিকে। ১৯৭৩ সালে লন্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দাউদ হায়দারের কোনো একটি কবিতাকে ‘দ্য বেস্ট পোয়েম অব এশিয়া’ সম্মানে ভূষিত করেছিল। সংবাদের সাহিত্য পাতায় ‘কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন তিনি। ধারণা করা হয়ে থাকে যে তিনি ওই কবিতায় হজরত মুহাম্মদ (সা.), যিশুখ্রিষ্ট ও গৌতম বুদ্ধকে অপমান করেছিলেন। তখন বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদী একটা গোষ্ঠী প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু করে এবং ঢাকার কোনো এক কলেজের শিক্ষক ঢাকার একটি আদালতে এই ঘটনায় দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ’৭৪-এর ২১ মে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ নির্দেশে কলকাতাগামী একটি ফ্লাইটে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়। ওই ফ্লাইটে তিনি ছাড়া আর কোনো যাত্রী ছিলেন না। তাঁর কাছে সে সময় ছিল মাত্র ৬০ পয়সা এবং কাঁধে ঝোলানো একটা ছোট ব্যাগ (ব্যাগে ছিল কবিতার বই, দুই জোড়া শার্ট, প্যান্ট, স্লিপার আর টুথব্রাশ)। কবির নিরাপত্তায় উদ্বিগ্ন ছিল সরকার? নাকি দেশে ধর্মীয় কারণে কোনো অস্থিতিশীলতা শুরু হোক, তা চায়নি? পরে ’৭৬-এ দাউদ হায়দার তাঁর পাসপোর্ট নবায়নের জন্য কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে জমা দিলে তা আটক করা হয়। স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এলে তিনি আটক পাসপোর্ট ফেরত চেয়ে আবেদন করেন। তাঁর পাসপোর্ট ফেরতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এরশাদ সরকারও। পাসপোর্ট ছাড়া অন্য আরেকটি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসে সমস্যা দেখা দেয়। ভারত সরকার দায়িত্ব নিতে চায় না নির্বাসিত কবির। দাউদ হায়দারকে ভারত থেকেও বহিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভারত সরকার তাঁকে ভারত ত্যাগের ফাইনাল নোটিশ দিয়ে দেয় এই বলে ‘… ইউ হ্যাভ নো কেইস ফর গ্রান্ট অব লংটার্ম স্টে ফ্যাসিলিটিজ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউ আর দেয়ারফর রিকোয়েস্টেড টু লিভ ইন্ডিয়া ইমিডিয়েটলি উইদাউট ফেইল।’ ১৯৮৫ সালে পেন আমেরিকান সেন্টারের ২০০০ লেখকের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লেখা হয় যাতে দাউদ হায়দারকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি অন্য কোনো দেশেও যেতে পারেন না পাসপোর্টের অভাবে। এমন এক দুঃখকালে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান কবিবন্ধু নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত কবিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ’৮৫-এর কোনো এক ভোরে জার্মানির বার্লিনে গিয়ে পৌঁছান দাউদ হায়দার। জাতিসংঘের বিশেষ ‘ট্রাভেল ডকুমেন্টস’ নিয়ে সেই থেকে আমৃত্যু ঘুরেছেন তিনি দেশান্তরে।
‘জন্ম আমার কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নার কালো বন্যায়
ভেসে এসেছি তোমাদের এই তিলোত্তমা শহরে
কল্পিত ঈশ্বর আমার দোসর; পায়ে তার ঘুঙুর; হৃদয়ে মহৎ পুজো
চুনকামে মুখবয়ব চিত্রিত; আমি তার সঙ্গী,
যেতে চাই মহিরুহের ছায়াতলে, সহি নদীজলে; ভোরের পবনে।
ঈশ্বর একান্ত সঙ্গী; জ্বেলেছি ধূপ লোবানের ঘরে। তার পায়ের ঘুঙুর সে
আমাকে পরিয়ে পালাল, আমি উঠলুম আমি।
ভেতরেও সে বাহিরেও সে; আমার আমি হয়ে চলেছি আমি,
মরণের নক্ষত্র দোদুল্যমান কালো ঘণ্টার রাজধানীতে বর্শার মতো দিন।
রাত্রির অলীক নটী, অন্ধদ্বন্দ্বে নাচায় ভাই; আমার বিশ্বাস ছিল
প্রতিধ্বনি নেই, তিমিরে আমার যাত্রা; দেখা হয় আলখেল্লায়
সজ্জিত মিথ্যুক বুদ্ধ; বসে আছে বোধিদ্রুমের ছায়াতলে;
যিশু আরেক ভন্ড; মোহাম্মদ তুখোড় বদমাশ; চোখেমুখে রাজনীতি,
আমি প্রত্যেকের কাছে পাঠ নিতে চাইলুম; তোমাদের চৈতন্যে যে লীলাখেলা
তার কিছু চাই এবেলা। দেখল ঈশ্বর, দেখল আদম।
আদমের সন্তান আমি; আমার পাশে আমি?
আমি আমার জন্ম জানি না। কীভাবে জন্ম? আতুরের ঘরে কথিত
জননী ছাড়া আর কে ছিল? আমায় বলেনি কেউ।
আমার মা শিখাল এই তোর পিতা, আমি তোর মাতা।
আমি তা–ই শিখেছি। যদি বলত, মা তোর দাসী, পিতা তোর দাস;
আমি তা–ই মেনে নিতুম। কিংবা অন্য কিছু বললেও অস্বীকারের
উপায় ছিল না।’