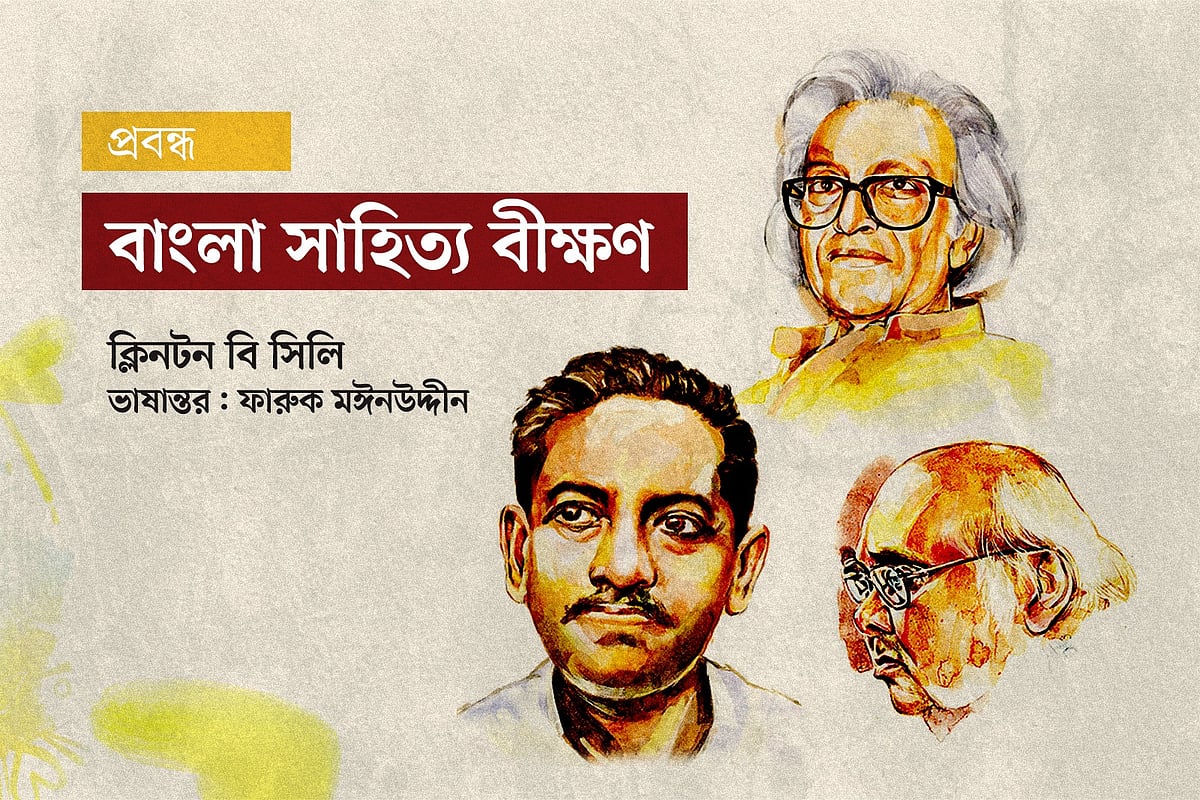
প্রবন্ধ
বাংলা সাহিত্য বীক্ষণ
ক্লিনটন বি সিলি | ভাষান্তর: ফারুক মঈনউদ্দীন
কোনো কিছু নিরীক্ষণ করা সহজ কাজ নয়। ধরা যাক, ইংরেজি ‘To view’ ক্রিয়াপদটিকে বাংলা করলে ‘দেখা’, ‘চোখে দেখা’, ‘চেয়ে দেখা’, ‘তাকিয়ে দেখা’, ‘দৃষ্টিপাত করা’, ‘লক্ষ্য করা’, ‘দর্শন করা’—এ রকম অনেক কিছুই হতে পারে। কিছুক্ষণের জন্য এসব অর্থের শেষটি, অর্থাৎ দর্শন করার ওপর আলোকপাত করা যায়। আপন বৈশিষ্ট্যে দর্শন শব্দটির একগাদা অর্থ আছে। আমরা যদি প্রাথমিক ‘দর্শন’ (শাস্ত্র) অর্থটি বাদও দিই, শব্দটি আরও বহুমাত্রার তাৎপর্য বহন করে। মোগল সম্রাট বাদশাহ আকবর ‘দর্শন দিতেন’।
‘প্রভাত হইবার পূর্ব হইতে তাঁহার উচ্চ-নিচ সকল শ্রেণীর প্রজাগণ বাহিরের চাতালে আসিয়া জড়ো হইতেন এবং তাঁহাদের নৃপতির উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতেন। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পর সকল শ্রেণীর প্রজাদের দেখা দিতেন তিনি, যাঁহারা আগ্রহভরে তাকাইয়া থাকিতেন তাঁহার “দর্শন” লাভের জন্য, যাঁহার ওপর নির্ভর করিত তাহাদের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য।’ [আকবর দ্য গ্রেট মোগল, ১৫৪২-১৬০৫, ভিনসেন্ট এ স্মিথ: (অক্সফোর্ড ক্লেয়ারডন প্রেস, ১৯১৭) ]
দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিতে ‘দর্শন দেওয়া’ বলতে বোঝায় ‘সাক্ষাৎ দেওয়া’ কিংবা ‘কোনো বক্তব্য শোনা’। তবে বাংলা কিংবা যেকোনো দক্ষিণ এশীয় ভাষায় ‘দর্শন দেওয়া’র আক্ষরিক অর্থ ‘দেখা দেওয়া’।
ইংরেজি ও দক্ষিণ এশীয় উভয় বাচনভঙ্গিতে একটা সামাজিক স্তরবিন্যাস ইঙ্গিত করে: উচ্চশ্রেণির মানুষেরা দর্শন দেন কিংবা শোনেন, আর নিম্নশ্রেণির মানুষেরা সেটা গ্রহণ করেন। ইংরেজি প্রকাশভঙ্গিতে এটা শ্রবণক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে পারে, আর দক্ষিণ এশীয় ভাষায় জোর দেওয়া হয় দেখা ও শোনার ওপর। তারপরও আরও মৌলিক পার্থক্য থেকে যায় দুই ভাষায় ব্যক্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে দর্শন লাভ করা গ্রহীতার জন্য হতে পারে কাঙ্ক্ষিত এবং বয়ে আনতে পারে ইতিবাচক ফল। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিতে দর্শন লাভ করা কেবল কাঙ্ক্ষিতই নয়, পুরস্কারযোগ্য, হিতকর এবং ফলদায়ী। হিন্দুধর্মের বিবেচনায় এটি এক পবিত্র ধর্মীয় কর্ম।২ যিনি দর্শন লাভ করেন, উপকৃত হন তিনি।
‘দেখা’ ক্রিয়াপদটার আলোচনায় ফিরে গেলে: এক অর্থে দক্ষিণ এশীয় ভাষায় ‘বাংলা সাহিত্য দেখা’ বলতে বোঝাতে পারে সেই সাহিত্যের দর্শনলাভ করা, অর্থাৎ কারও ওপর দর্শন লাভের সহজাত উপকার কিংবা আনুকূল্য বর্ষিত হতে দেওয়া। আমাদের যাঁরা বাংলা সাহিত্য পড়েন, সে হিসেবে বলা যায়, তাঁরা সেটির দর্শন লাভ করছেন। যা-ই হোক, ‘দেখা’ বলতে নিশ্চিত করে ‘দর্শনলাভ’ বোঝায় না। ইংরেজি ভাষ্যে ‘to view as’ কিংবা ‘to view in a positive light’ অথবা ‘to view with a jaundiced eye’ বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় ‘বিশেষ দৃষ্টিতে’ কিংবা ‘ইতিবাচকভাবে’ অথবা ‘অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখা’। অথচ ‘দর্শনলাভ করা’ বললে দৃষ্ট বিষয় তার অখণ্ডতা ধরে রাখে, অন্যদিকে দ্রষ্টার মধ্যে ঘটে পরিবর্তন (লাভবান হয়)। কারও ‘দৃষ্টিতে’ বললে হয় তার উল্টোটা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে দৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিজের সৃষ্ট মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা দেন দ্রষ্টা।
আমরা সবাই জানি, দেখার কাজটি সরল বিশ্বাসে করা হলেও কখনোই সম্পূর্ণ, বিশদ ও নিখুঁত হয় না। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের ‘কিম’ উপন্যাসের নামচরিত্র কিমকে শিখিয়ে দিতে হয়েছিল, যাতে সে সিমলায় লারগ্যান সাহেবের কিউরিও শপের জিনিসপত্র আরও বেশি করে লক্ষ করে, কারণ ব্রিটিশদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল সে, যেটাকে বলা হতো ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ ও সংহত করার বড় খেলা। কিউরিও শপটা কলকাতার আশপাশে নয়, হিমালয়ের একটা হিল স্টেশন সিমলায়। একইভাবে আমাদের স্মরণ করানোর দরকার নেই যে কিপলিংয়ের উপন্যাসটা রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসে আমরা যে রকম দেখি, তার চেয়ে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখা ভারতকে উপস্থাপন করে। একমাত্র মিল উভয় উপন্যাসের নামীয় নায়কদের মধ্যে: দুজনই গত শতাব্দীতে আইরিশ মা-বাবার এতিম সন্তান। ‘ভিন্নদৃষ্টিতে দেখা ভারত’ বলতে স্বভাবতই আমরা বুঝি, কিপলিংয়ের ভারত (কেবল ভারত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নয়) রবীন্দ্রনাথের ভারতের চেয়ে আলাদা, কারণ, এই উভয় ক্ষেত্রের দ্রষ্টারা দর্শন লাভকারী মানুষের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট বিষয়কে সৃষ্টি করে সুবিধামতো ব্যবহার করেন।
দৃষ্ট বিষয়কে ‘সুবিধামতো ব্যবহার’ করার বিষয়টা খোলাসা করি। প্রায় সংজ্ঞাগতভাবে সাহিত্য সৃষ্ট হয় লেখকদের দ্বারা সুবিধামতো ব্যবহার করা নির্মিত বয়ানে, নিজের বাস্তবতাকে সৃষ্টি করেন তাঁরা। শামসুর রাহমানের ‘ক্ষয়কাশ’ কবিতায় তাঁর দেখা ঢাকার কথা উল্লেখ করতে পারি আমরা:
কে যেন উঠলো কেশে কলোনির ফ্ল্যাটে খক্খকিয়ে,
যে মোটর কিছুতে নেয়না স্টার্ট ঠিক তারই মতো
শব্দ করে ঠান্ডা রাতে কাশছে লোকটা অবিরত।
গলিপথে অন্য কেউ কেশে ওঠে, প্রাণক্ষয়ী কাশ—
পাশের দালানে কেউ, কেউ বা মাটির ভাঙা ঘরে
বস্তিতে বাজারে আর অভিজাত পাড়ার অন্দরে,
ভয়াবহ শব্দে সেই ছেয়ে গেল সমস্ত আকাশ।
ন্যূনতম নব্বুই হাজার বাসগৃহে নিদ্রাহর
শব্দের ধমকে নড়ে সংখ্যাহীন বুকের পাঁজর
এবং আমার বুক পূর্ব বাংলার মতোই হু হু, তীব্রতর
কাশির দমকে বড্ড দুমড়ে যাই, কুঞ্চিত চাদর
গোধূলি-তরল রক্তে বারংবার ওঠে ঝক্ঝকিয়ে।
দৃশ্যের এ রকম জীবন্ত চিত্রায়ণ, পয়ার ছন্দের মসৃণ প্রবাহ এবং সমাপ্তিসূচক শক্তিশালী চিত্রকল্প সত্ত্বেও কবিতাটি পাঠকের চোখে তুলে ধরতে পারে কিছুটা হতাশাজনক, অসুস্থ ঢাকাকে। উপরন্তু এ রকম একটা ধারণা আমেরিকায় বরং সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণার একটা উদাহরণ। মরণাপন্ন মানুষদের জন্য কলকাতায় মাদার তেরেসার সেবা সদনটার কথা মনে পড়ে যায় তাৎক্ষণিক। এ বছর (১৯৯২-৯৩) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক বাংলা পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়া আটজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছয়জনই বাঙালি-আমেরিকান কিংবা দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি অথবা নিজেদের বহুজাতিক বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করা বাঙালি, কিংবা ঘরে কিছু বাংলা বলে থাকেন এমন হাইফেনবর্জিত আমেরিকান, যেহেতু তাদের মধ্যে অন্যরা নিজেদের এভাবেই পরিচয় করান। অনেকের মধ্যে এসব তরুণের বাংলাদেশ সফরের একটা সাধারণ ধারণা হচ্ছে, এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা। সেটা অবশ্য আমরা যা বাস্তব বলে ভাবি তার একটা অংশ, একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একটা অংশ কেবল।
ঢাকার সেই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত দৃশ্যের বিপরীতে শামসুর রাহমান অনেক বেশি ইতিবাচক, আকর্ষণীয় স্বস্তিকর জায়গা হিসেবে ইতিহাস-সমৃদ্ধ, স্মৃতিবাহী বাখরখানির সুঘ্রাণযুক্ত নগরীটির বহু বর্ণনা চিত্রিত করেছেন। কিশোরদের জন্য তাঁর স্মৃতির শহর এ রকমই একটা গদ্যের বই। উভয় রচনাই শামসুর রাহমানের দেখা ঢাকার দৃশ্য—এসব লেখায় ভিন্ন ভিন্ন আবহ আনার জন্য নিজের মতো করে ব্যবহার করা হয়েছে আপন সৃষ্ট ঢাকাকে।
১৯৭৮ সালে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির তৎকালীন অধ্যাপক এবং জাতিগতভাবে একজন প্যালেস্টাইনি এডওয়ার্ড সাঈদ প্রকাশ করেন শতাব্দীর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী বইগুলোর একটি। আমরা আগে যেটিকে প্রাচ্য বলতাম এবং তার বিপরীতে যেটিকে পাশ্চাত্য নামে অভিহিত করা হয়, এই উভয় বিশ্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয় ‘ওরিয়েন্টালিজম’ নামের এই বইটি। এই দুই সত্তার মধ্যকার সম্পর্ককে ক্ষমতার নিরিখে বর্ণনা করা যায়, পাশ্চাত্য হচ্ছে কর্তৃত্বময় এবং আধিপত্যবাদী। সাঈদ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভেতরকার সম্পর্ক বিষয়ে এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দেন আমাদের (কেউ বলবেন উত্তরাধুনিক কিংবা উপনিবেশ-উত্তর অথবা নব্য ইতিহাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি), যে সম্পর্ক এই স্বতঃসিদ্ধের ওপর স্থাপিত, যে ভাষা কখনোই রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হতে পারে না, জ্ঞানই শক্তি এবং কোনো বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলা মানে এক অর্থে সেই বিষয় বা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং এমনকি সৃষ্টি করা। সাঈদকে উদ্ধৃত করছি:
‘প্রাচ্যের মানুষদের জগতের বোধগম্যতা ও স্বকীয়তা তাদের নিজের চেষ্টায় অর্জিত নয়, সেটা এসেছে বরং [পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের ওপর] অভিজ্ঞ, স্বার্থমুখী একগুচ্ছ প্রভাবের মাধ্যমে, যা দিয়ে প্রাচ্যকে চিহ্নিত করে পাশ্চাত্য বিশ্ব।... শক্তি থেকে উৎসারিত প্রাচ্যের জ্ঞান এক অর্থে সৃষ্টি করে প্রাচ্য, প্রাচ্যজন এবং তার জগৎকে।’
একটা অকাট্য উদাহরণ হিসেবে ফ্লবেয়ার এবং এক প্রাচ্যদেশীয় রমণীর কথা লেখেন সাঈদ:
ফ্লবেয়ারের সঙ্গে জনৈক অভিজাত মিসরীয় বারাঙ্গনার পরিচয় প্রাচ্য নারীদের যে প্রভাবশালী নমুনা তৈরি করে, সে নারী নিজের সম্পর্কে কখনো কিছুই বলে না, কখনো প্রকাশ করে না নিজের আবেগ, উপস্থিতি বা ইতিহাস। সেই নারীর হয়ে কথা বলেন, প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। ফ্লবেয়ার বিদেশি, তুলনামূলকভাবে বিত্তবান ও পুরুষ—এসবই আধিপত্যের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, যা কেবল কুচুক হানেমকে দৈহিকভাবে অধিকারে সক্ষমই করে না তাঁকে, হানেমের পক্ষে কথা বলার এবং কোন দিক দিয়ে ‘খাঁটি প্রাচ্য’ নারী সে, তা পাঠককে জানানোর ক্ষমতাও দেয়। আমার যুক্তি হলো, কুচুক হানেমের তুলনায় ফ্লবেয়ারের অবস্থান কোনো একক বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়, এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক শক্তির বিন্যাস এবং সেটা থেকে সক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাচ্যবিষয়ক ডিসকোর্সের একটা আদর্শ উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।
‘ওরিয়েন্টালিজম’ বইয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কের প্রতি পুনর্দৃষ্টি দিতে এগিয়ে আসেন সাঈদ এবং দেখাতে চান, কীভাবে ইউরোপ তাঁর বইপত্রের মাধ্যমে সেসব প্রাচ্যের দেশ, মানুষ এবং সংস্কৃতিকে ইউরোপের জন্য নির্মাণ করেছে ইউরোপীয়দের মনে। এঁরা ছিলেন প্রথম অনুসন্ধানকারী, পরিব্রাজক, দুঃসাহসী অভিযাত্রিক এবং তারপর পরবর্তী সময়ের ঔপনিবেশিক শাসক এবং পণ্ডিত ইউরোপীয় গ্রন্থকার—যাঁরা দেশে ফেরা স্বদেশবাসীর জন্য সেই ‘অদ্ভুত’ দেশসমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এঁরা ছিলেন সেই ইউরোপীয় লেখক, যাঁরা প্রাচ্যকে ‘দেখেছেন’ এবং সেসব দেশের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁদের মতামত পৌঁছে দিয়েছেন দেশবাসীর কাছে, (বর্তমানের উত্তরাধুনিক ভাষায় তাঁদের বলা হয় ‘the Other’)। এরা হচ্ছে সেই ইউরোপীয়, যারা প্রাচ্য ও প্রাচ্যদেশীয় মানুষের হয়ে কথা বলেছে, তবে তাদের নিজেদের কথা বলতে দেয়নি। সেসব কর্তৃত্ববাদী ইউরোপীয়রা এক অর্থে নিজেদের মতো ব্যবহার করেছে তাদের দেখা প্রাচ্য এবং প্রাচ্যদেশীয় মানুষদের, আর ইউরোপের জন্য সৃষ্টি করেছে নিকৃষ্ট এক প্রাচ্যদেশ, যাদের প্রয়োজন সদাশয় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ।
প্রাচ্যকে দেখার পর তাকে সৃষ্টি করা ছিল আত্মসাৎ করার মতো, কারণ, প্রাচ্য তখন পরিণত হয়েছিল তার স্রষ্টার সম্পত্তিতে, অনেকটা যেমন দখল করা হয়েছিল ফ্লবেয়ারের রক্ষিতা কুচুক হানেমকে। দেখার কাজটি ছিল একধরনের ঈক্ষণকাম, যেটা শহীদ কাদরীর ‘নগ্ন’ শিরোনামের কবিতাটিতে যা ঘটে তার চেয়ে অনেক বেশি বিসদৃশ ছিল না:
বারান্দার ত্রিভুজ কোণে
খোলা জানালার সারি শিকের ফাঁক থেকে
দেয়ালের ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে
হতাশার একটি রন্ধ্র দিয়ে
সন্তের নিঃসঙ্গতায় দাঁড়িয়ে
নিষ্কাম ভাঁড়ের বিস্ময়ে
মরণের টানেল থেকে
ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়
দেখি স্নানরত
একটি নারী,
নগ্ন।
শহীদ কাদরীর কবিতাটা যে প্রবণতা থেকে উদ্ভূত, তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ দাশের ‘নগ্ন নির্জন হাত’ কবিতাটাও:
আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে:
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।
যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনো দিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।
মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।
ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ;
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরি শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘর পল্লব ছিল অনেক;
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল;
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কতশত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।
ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলানও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের
ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।
পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।
শহীদ কাদরী ও জীবনানন্দ দাশ—দুজনই অবলোকন করেন এবং আমাদের জন্য সৃষ্টির কাজে নিমগ্ন হন, তারপর একটা বাণীর মাধ্যমে জানান বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, সব বাস্তবতা নয়, তার কিছু অংশ। আমরা এই উপসংহারে আসতে চাইতে পারি যে জীবনানন্দ অনেক বেশি সৃষ্টি করেন, কারণ, কল্পনার মধ্যেই স্পষ্টভাবে বিরাজ করে তাঁর ভুবন। তবে এমনও বলার কিছু নেই যে শহীদ কাদরীর সৃষ্টি কল্পনার চেয়ে কোনো অংশে কম, যদিও এটাকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। দুটো কবিতাই কোনোভাবে ঈক্ষণকামী। দুটো কবিতাতেই কথক ব্যক্তিকে দেখেন স্বপ্নসৌধের ভেতর দিয়ে (লক্ষণার মাধ্যমে যেভাবে জীবনানন্দের কবিতায় ‘হাত’ বলতে বোঝাচ্ছে সম্পূর্ণ মহিলাটিকে) উভয় কবিতায় যাকে লক্ষ করা হচ্ছে সে একজন নারী। আমরা এমনও বলতে চাইতে পারি, যে অভীষ্ট ব্যক্তিকে দেখা হচ্ছে, সে নারী, কারণ তাকে অভীষ্টায়িত করা হয়েছে। কথক এবং কবিতার নারীদের মধ্যে কোনো মানবীয় মিথস্ক্রিয়া নেই। তারা কেবল রয়েছে দৃষ্টির গোচরে।
নারীবাদী সমালোচকেরা ‘নজর’ কিংবা নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের বিষয়ে ইঙ্গিত করে অনুযোগপূর্ণ কথা বলেছেন পুরুষের নজর সম্পর্কে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর সম্পর্কে একজন পুরুষের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে পুরুষের নজর সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। পটভূমিটা ছিল এক সম্মেলন—১৯৮৬ সালের জানুয়ারির সাবঅলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন—যেখানে গায়ত্রী এবং মহাশ্বেতা দেবী দুজনই শেষোক্তজনের ছোটগল্প ‘স্তনদায়িনী’র ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। ডেভিড হার্ডিম্যান এই সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর বর্ণনায় মহাশ্বেতা দেবীর ভণিতাবিহীন শৈলীর কথা লিখেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি স্পিভাককেও ‘ছাড়িয়ে গেছেন,’ যার প্রতিবাদে স্পিভাক লেখেন, ‘তারপরও আমি বলব যে হার্ডিম্যানের ভঙ্গি পরিষ্কারভাবে পুরুষতান্ত্রিক: তাকানোর বিষয় বানিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করে নারীদের।’
শহীদ কাদরীর কবিতার কথক যেভাবে একদৃষ্টে তাকায়—যদিও খুব সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবে—কিংবা শব্দটির নারীবাদী অর্থে যেভাবে তাকিয়ে থাকে, সেটা বহুভাবে উত্তরা আধুনিক সমালোচকদের দৃষ্টিতে দেখা প্রাচ্যের প্রতি ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। ইউরোপ তাকিয়ে ছিল প্রাচ্যের দিকে। এই তাকিয়ে থাকা তখন আর দর্শনপ্রাপ্তি নয়, কারণ, দর্শন দেয় উচ্চশ্রেণি, আর নিম্নশ্রেণি গ্রহণ করে সেটা। ‘ওরিয়েন্টালিজম’ বইতে সাঈদ দেখান, ইউরোপ কখনোই হীন বলে মনে করেনি নিজেকে।
এ পর্যন্ত আমি দুই ভিন্ন মেরুর দ্রষ্টাদের মেলাতে চেষ্টা করে আসছি। তাঁরা হচ্ছেন এক কবি তাঁর নিজের জাতিগত সাংস্কৃতিক ভুবনকে দেখে সে সম্পর্কে লিখছেন, আরেকজন নিজের নয় এমন সংস্কৃতিকে দেখে সেটা নিয়ে লিখছেন, সাঈদ যাকে বলছেন ‘প্রাচ্যবাদী’। স্বীকার করছি এই দুটো প্রসঙ্গ সত্যিকারভাবে তুলনাযোগ্য নয়। তার ওপর, আমি বলে আসছি দুই ধরনের দেখার কথা: একটা দেখায় ‘দর্শনলাভ,’ আরেকটা ‘অবলোকনে রত হওয়া’। একইভাবে এই দুই উপায়ে দেখায় একটির সঙ্গে আরেকটির অসামঞ্জস্য আছে। এবার আমি ‘বাংলা সাহিত্য বীক্ষণ’ বিষয়ে দৃষ্টি ফেরাই, যেটি আমার এই প্রবন্ধের শিরোনাম।
প্রায় ২৫ বছর ধরে বাংলা সাহিত্য পড়ছি আমি। এই সাহিত্য কিংবা তার কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ, যেমন কবিতা অথবা কোনো বিশেষ কবি সম্পর্কে প্রায়ই আমার মতামত জানতে চাওয়া হয়, অর্থাৎ ভূমিকা পালন করতে হয় একজন সাহিত্য সমালোচকের। মাঝেমধ্যে কখনো মূল্য বিচার করে মতামত দিয়েছি আমি। কিন্তু সাঈদ-উত্তর সময়ে আমরা যাঁরা অচেনা সংস্কৃতিজাত সাহিত্য পড়ি, তাঁদের নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হয়: কেমন ধরনের দ্রষ্টা আমরা এবং কোন ধরনের বীক্ষণ অনুশীলন করছি? সাহিত্য সমালোচক কবি হতে পারেন না, কারণ, তাঁরা মৌলিকভাবে আলাদা সত্তা, একজন (সমালোচক) নির্ভরশীল অন্যজনের (কবি) ওপর। কবির সৃষ্টিই সমালোচকের জন্য হয়ে ওঠে পর্যালোচনার বিষয়বস্তু। কবিতা না থাকলে সমালোচকও থাকতে পারেন না। সুতরাং কবির ছাঁচে দ্রষ্টা হতে পারি না আমরা। তবে আমরা হতে পারি প্রাচ্যদেশীয়। এ কারণেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার বিরুদ্ধে।
এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা যুক্তি দেখাবেন যে সাহিত্য বিশ্বজনীন, মানুষের আবেগ সব মানবতার জন্য প্রযোজ্য, তাই সাহিত্য এবং তার মূল্যায়ন ছাড়িয়ে যায় সব ছায়ারেখাকে, দেশের সীমান্তরেখাকে যে নামে অভিহিত করেন ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষ। এই যুক্তি অনুযায়ী, নন্দনতত্ত্বের সর্বজনীনতা রয়েছে, যা বিশ্বের সব সাহিত্যের জন্য প্রযোজ্য করে তোলা উচিত সাহিত্য সমালোচকের। সংস্কৃতির সাঈদ-উত্তর তাত্ত্বিকেরা বলেন, ব্যাপারটা সে রকম নয়। ‘বিশ্বজনীনতার শব্দকোষ: পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার বিশ্বজনীনবাদী মাপকাঠির সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ’ শিরোনামের প্রবন্ধে অরুণ মুখোপাধ্যায় বিষয়টা নিয়ে লেখেন: ‘উদারপন্থী মানবতাবাদী সমালোচকদের দাবির বিপরীতে সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যিক মূল্যায়ন সংস্কৃতিনির্ভর, সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্বিশেষে প্রয়োগ করা যায়, এমন কোনো বিশ্বজনীন মানদণ্ড প্রণয়ন করা সম্ভব নয়।’ কেউ ভাবতে পারেন অরুণ মুখার্জী একজন পুরুষ, যদিও বাংলায় অরুণ একজন পুরুষের নাম, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন পাঞ্জাবি-কানাডীয় নারী, টরন্টোর ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি পড়ান তিনি, বিয়ে করেছেন এক বাঙালি-কানাডীয় ভদ্রলোককে। তিনি বলেন, বিশ্বজনীনতাবাদী মাপকাঠি, অর্থাৎ বিশ্বজনীনতাবাদী বলে দাবি করা পাশ্চাত্য মানদণ্ড হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী মানদণ্ড কিংবা সাঈদের পরিভাষায় প্রাচ্যবাদী।
সৌভাগ্যবশত মুখার্জী কেবল বাংলা সাহিত্যের ‘দর্শন পাওয়ার জন্য’ বাংলা সংস্কৃতিতে জন্মগ্রহণ না করা আমাদের সবার নিন্দা করেননি, যদিও সেটা করতে পেরে আমি বেশ সন্তুষ্ট। তিনি মনে করেন, আমাদের ‘সাংস্কৃতিক অন্তরঙ্গতা’ অর্জন করা প্রয়োজন, যার দ্বারা তিনি আমাদের বোঝাতে চান আমরা যাতে সাহিত্যের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হই, যার বিষয়ে সমালোচক হিসেবে মন্তব্য করতে পারি আমরা এবং সচেতন হই কীভাবে বাঙালি সমালোচক ও পাঠকেরা দেখেন আলোচিত সাহিত্যকে। এই অতিবিচক্ষণ প্রস্তাবের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত পোষণ করি আমি। এই বক্তৃতায় ব্যবহার করা উদ্ধৃতিগুলোই বলে দেবে নিজেদের কথা। আমার বাছাই করা শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা আপনাদের বলে দেবে যে তাঁদের শিল্পকে মূল্যায়ন করি আমি। আমার বিশ্বাস, বাঙালি পাঠক হিসেবে একমত হবেন আপনারাও।
[ক্লিনটন বি সিলির ‘বরিশাল অ্যান্ড বিয়ন্ড’ বইয়ের প্রকাশিতব্য বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত]